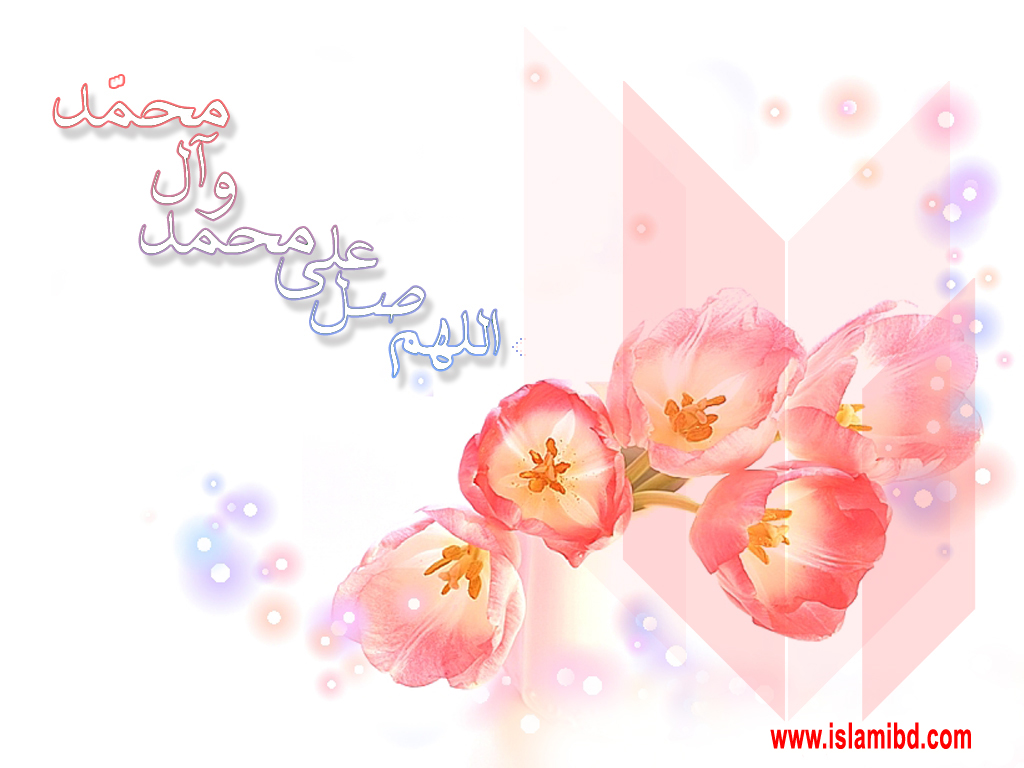রাসুলুল্লাহর (সাঃ) আহলে বাইত ও বিবিগণ
আলোচনার মানদণ্ড
অত্র আলোচনার শুরুতে আমরা দ্বীনী বিষয়াদিতে আলোচনার ক্ষেত্রে সর্বজনগ্রহণযোগ্য অকাট্য মানদণ্ড সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করতে চাই। কারণ, আমরা যাতে সন্দেহাতীত উপসংহারে উপনীত হতে পারি সে লক্ষ্যে আমাদেরকে কেবল ঐ সব মানদণ্ডের ভিত্তিতে আলোচনা করতে হবে যেগুলো অকাট্য এবং মাযহাব ও ফির্ক্বাহ্ নির্বিশেষে সকল মুসলমানের কাছে সমভাবে গ্রহণযোগ্য হওয়া অপরিহার্য।
মাযহাব ও ফির্ক্বাহ্ নির্বিশেষে সকল মুসলমানের জন্য দ্বীনী বিষয়াদিতে আলোচনার ক্ষেত্রে যে সব মানদণ্ড অকাট্যভাবে গ্রহণযোগ্য হওয়া অপরিহার্য সেগুলো হচ্ছে ‘আক্বল্ (বিচারবুদ্ধি), কোরআন মজীদ, মুতাওয়াতির হাদীছ ও ইজ্মা ‘এ উম্মাহ্।
সংক্ষেপে বলতে হয়, ‘আক্বল্-কে এ কারণে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে যে, তা সমস্ত মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য সর্বজনীন মানদণ্ড যার ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে একজন অমুসলিম ইসলামের সত্যতায় উপনীত হয় ও তা গ্রহণ করে এবং কোরআন মজীদ সহ অন্য সমস্ত জ্ঞানসূত্র থেকে সঠিক তাৎপর্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ‘আক্বল্ সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।
অন্যদিকে আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সর্বশেষ, পূর্ণাঙ্গ ও সংরক্ষিত কিতাব হিসেবে কোরআন মজীদকে মুসলমানদের জন্য মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণের অপরিহার্যতা সম্পর্কে আলাদা কোনো দলীল উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই। কারণ, কেউ যদি কোরআন মজীদকে অকাট্য মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ না করে তাহলে তার ঈমানই থাকে না।
আর যেহেতু মুতাওয়াতির হাদীছ হচ্ছে তা-ই যা ছাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে গ্রন্থাবদ্ধকরণ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে এতো বেশী সংখ্যক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত হয়েছে মিথ্যা রচনার জন্য যত লোকের পক্ষে একমত হওয়া বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয় সেহেতু এ ধরনের হাদীছ যে সত্যি সত্যিই হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) থেকে এসেছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।
এছাড়া যে সব আমল বা যে সব হাদীছ হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর পর থেকে ধারাবাহিকভাবে মাযহাব ও ফির্ক্বাহ্ নির্বিশেষে মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়ে এসেছে উপরোক্ত তিন সূত্রের কোনোটির সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) থেকে চলে আসার ক্ষেত্রে তার নির্ভুলতা সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ নেই।
এর বাইরে খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছ ও ইসলাম বিশেষজ্ঞ মনীষীদের মতামত কেবল উক্ত চার সূত্রের কোনোটির সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষেই গ্রহণযোগ্য। অবশ্য সেই সাথে, পরস্পর বিরোধী দুই বা বিভিন্ন চৈন্তিক গোষ্ঠীর কোনোটির সূত্রে যদি তার বিরোধী কোনে চৈন্তিক গোষ্ঠীর দাবীর সপক্ষে কোনো দলীল থাকে সে ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির কাছে উক্ত দলীলের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।
তবে অত্র আলোচনায় আমরা প্রধানতঃ ‘আক্বল্ ও কোরআন মজীদের ভিত্তিতেই ফয়সালায় উপনীত হবার জন্য চেষ্টা করবো। কারণ, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যথাসম্ভব সংক্ষেপে অকাট্য ফয়সালায় উপনীত হওয়া। এ ক্ষেত্রে অবশিষ্ট দলীলগুলোর আশ্রয় নিতে গেলে আলোচনা শুধু দীর্ঘই হবে না, বরং অবিতর্কিত ফয়সালায় উপনীত হওয়াও বেশ কঠিন হয়ে পড়তে পারে। কারণ, এমনকি কোনো মুতাওয়ার্তি হাদীছ সম্পর্কেও কেউ তার মুতাওয়ার্তি হওয়ার ব্যাপারে সন্দহ প্রকাশ করতে পারে। ফলে এরূপ সম্ভাব্য সন্দেহ মোকাবিলার জন্য অনেক বেশী বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন হয়ে পড়ে; খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা তো খুবই সাধারণ ব্যাপার, বিশেষ করে যখন পরস্পর বিরোধী হাদীছের অস্তিত্ব থাকে।
সর্বোপরি, যদি ‘আক্বল্ ও কোরআন মজীদ কোনো বিষয়ে অকাট্য ফয়সালায় উপনীত হবার জন্য যথেষ্ট হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে অন্যান্য দলীলের দ্বারস্থ হয়ে আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি করার কোনোই যৌক্তিকতা নেই।
কোরআন মজীদে রাসুলুল্লাহর (সাঃ) আহলে বাইত্ ও বিবিগণ
আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীন কোরআন মজীদের সূরাহ্ আল্-আহযাবের ২৮ নং আয়াত থেকে ৩৩ নং আয়াতের প্রথমাংশ পর্যন্ত হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর বিবিগণ সম্পর্কে নির্দেশাদি দিয়েছেন এবং এরপর ৩৩ নং আয়াতের দ্বিতীয়াংশে আহলে বাইতের কথা উল্লেখ করেছেন। আয়াতগুলো হচ্ছে ঃ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا2وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا30وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا31يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا32وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
“হে নবী! আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য (ভোগ-বিলাসিতা) কামনা কর তাহলে এসো, আমি তোমাদেরকে ভোগ্য উপকরণাদির ব্যবস্থা করে দেই এবং তোমাদেরকে উত্তমভাবে বিদায় করে দেই। আর তোমরা যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে এবং পরকালের গৃহকে কামনা কর তাহলে অবশ্যই (জেনো যে,) আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যকার উত্তম কর্ম সম্পাদনকারীদের জন্য মহাপুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। হে নবী-পতœীগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যে প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ করবে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে এবং এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে এবং নেক আমল সম্পাদন করবে সে জন্য তাকে আমি দুই বার পুরষ্কার প্রদান করবো এবং আমি তার জন্য সম্মানজনক রিয্ক্ব প্রস্তুত করে রেখেছি। হে নবী-পতœীগণ! তোমরা অন্য কোনো নারীর মতো নও; (অতএব,) তোমরা যদি তাক্বওয়া অবলম্বন করে থাকো তাহলে তোমরা (পরপুরুষদের সাথে) তোমাদের কথায় কোমলতার (ও আকর্ষণীয় ভঙ্গির) আশ্রয় নিয়ো না, কারণ, তাহলে যার অন্তরে ব্যধি আছে সে প্রলুব্ধ হবে। বরং তোমরা স্বাভাবিকভাবে কথা বলো। আর তোমরা গৃহে অবস্থান করো এবং পূর্বতন জাহেলীয়াত-যুগের সাজসজ্জা প্রদর্শনীর ন্যায় সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না। আর তোমরা নামায কায়েম রাখো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। হে আহলে বাইত্! আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের থেকে অপকৃষ্টতা অপসারিত করতে এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে পূতপবিত্র করতে চান।”
এখানে সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ৩৩ নং আয়াতের শেষাংশে আহলে বাইত্কে সম্বোধন করে কথা বলার পূর্ব পর্যন্ত আলোচনা ও নির্দেশাদির লক্ষ্য হচ্ছেন হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর বিবিগণ। নবী করীম (সাঃ)কে সম্বোধন করে তাঁর ‘স্ত্রীগণকে’ বলার জন্য নির্দেশ দান, এরপর সরাসরি তাঁদেরকে ‘হে নবী-পতœীগণ!’ বলে সম্বোধন এবং তাঁদেরকে বুঝাতে کُنتُنَّ, تُرِدنَ, مِنکُنَّ ইত্যাদিতে বহুবচনে স্ত্রীবাচক সংযুক্ত সর্বনাম ব্যবহার থেকে এ ব্যাপারে কোনোই সন্দেহের অবকাশ থাকছে না। কিন্তু ৩৩ নং আয়াতের শেষাংশে আহলে বাইত্কে সম্বোধন করে কথা বলার ক্ষেত্রে عَنکُم ও يُطَهِّرَکُم বলা হয়েছে যাতে বহুবচনে পুরুষবাচক সংযুক্ত সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে। আর আরবী ভাষায় বহুবচনে দু’টি ক্ষেত্রে পুরুষবাচক সর্বনাম ব্যবহার করা হয় ঃ শুধু পুরুষ বুঝাতে এবং নারী ও পুরুষ একত্রে বুঝাতে।
অতএব, এ থেকে সুস্পষ্ট যে, এখানে “আহলে বাইত্” কথাটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। কারণ, যেহেতু হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর পরিবারে কেবল তাঁর স্ত্রীগণ ছিলেন; কোনো নাবালেগ (এমনকি সাবালেগও) পুরুষ সন্তান ছিলেন না, সেহেতু “আহলে বাইত্” কথাটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করা হলে আগের মতোই বহুবচনে স্ত্রীবাচক সম্বোধন ব্যবহার করা হতো। অতএব, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এখানে কথাটি বিশেষ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আর সে অর্থে নারী ও পুরুষ উভয়ই হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর আহলে বাইত-এর মধ্যে শামিল রয়েছেন।
দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, আহলে বাইত্-এ শামিলকৃত পুরুষ সদস্য কে বা কা’রা এবং নারী সদস্যই বা কে অথবা কা’রা? এ নারী সদস্য কি হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর বিবিগণ, নাকি অন্য কেউ, নাকি তাঁর বিবিগণের সাথে অন্য কেউ?
এখানে আমাদেরকে আয়াতের বক্তব্যের ও তার বাচনভঙ্গির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।
উল্লিখিত আয়াত সমূহে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর বিবিগণ সম্পর্কে এবং তাঁদেরকে সম্বোধন করে যে সব কথা বলা হয়েছে তাতে তাঁদেরকে কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, বরং চরম পত্র দেয়া হয়েছে, কয়েকটি বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে এবং কয়েকটি বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়েছে। চরম পত্রের বিষয় হচ্ছে এই যে, তাঁরা পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য (ভোগ-বিলাসিতা) কামনা করলে তাঁদেরকে বিদায় করে দেয়া হবে। এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাঁরা পার্থিব উপায়-উপকরণাদির জন্য হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন।
এছাড়া তাঁদেরকে পরবর্তী বক্তব্যে যে সব বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে ও নিষেধ করা হয়েছে সে সব বিষয়ে কোরআন মজীদের অন্যত্র সাধারণভাবে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সকল মু’মিনা নারীকেই সতর্ক ও নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু এ সত্ত্বেও নবী-পতœীগণকে স্বতন্ত্রভাবে সতর্কীকরণ ও নিষেধকরণ থেকে এ ইঙ্গিত মিলে যে, অন্য মু’মিনা নারীদের মতোই তাঁদের ঐ সব বিষয় থেকে মুক্ত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত নয়, কিন্তু রাসূলের (সাঃ)-এর বিবি হিসেবে তাঁর মর্যাদার সাথে জড়িত বিধায় তাঁদের এ সব থেকে মুক্ত থাকা অনেক বেশী প্রয়োজন এবং এ কারণেই তাঁদেরকে আলাদাভাবে সতর্ক করা ও নিষেধ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। সুস্পষ্ট যে, একই অপরাধ করলে সাধারণ মু’মিনা নারীর তুলনায় তাঁদের দ্বিগুণ শাস্তি দেয়ার ফয়সালার কারণও এটাই যে, তাঁদের আচরণের সাথে রাসূলের (সাঃ) ব্যক্তিগত মর্যাদা ও আল্লাহর দ্বীনের মর্যাদা জড়িত।
এখানে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, বিদায় করে দেয়ার হুমকির ক্ষেত্রে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর বিবিগণের সকলকে একত্রে শামিল করা হয়েছে যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ ব্যাপারে দাবী তোলা বা চাপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁরা সকলেই শামিল ছিলেন।
যদিও, উল্লেখ না করলে নয় যে, স্ত্রী বা স্ত্রীগণ স্বামীর কাছে স্বাভাবিক ভরণ-পোষণ ও ভোগোপকরণ ‘দাবী’ করলে, এবং এমনকি তার অতিরিক্ত অলঙ্কারাদি ও আরাম-আয়েশের উপকরণাদির জন্য ‘আবদার’ করলে তা গুনাহ্র কাজ নয়, তেমনি স্বামীর জন্যও স্ত্রীকে বা স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়া নাজায়েয নয়। কিন্তু রাসূলের (সাঃ) বিবি হওয়ার মর্যাদার এটাই দাবী ছিলো যে, তিনি যা কিছু দিতে সক্ষম তার চেয়ে বেশী দাবী করে (এমনকি বৈধ হলেও) তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করা হবে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও চাপ সৃষ্টি করা হলে তা আল্লাহ্ তা‘আলার পসন্দনীয় হয় নি।
কিন্তু গুনাহ্র জন্য শাস্তির ভয় দেখানো ও নেক আমলের পুরষ্কারের সুসংবাদের বিষয়গুলোতে তাঁদের সকলকে সম্মিলিতভাবে শামিল না করে প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে সতর্ক করা হয়েছে ও সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।
অতঃপর আহলে বাইত্ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে ঃ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
“হে আহলে বাইত্! আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের থেকে অপকৃষ্টতা অপসারিত করতে এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে পূতপবিত্র করতে চান।”
আয়াতের এ অংশে ব্যবহৃত শব্দাবলীর প্রতি সতর্কতার সাথে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে, এখানে আল্লাহ্ তা‘আলা আহলে বাইত্কে সম্বোধন করলেও হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর বিবিগণের ন্যায় তাঁদেরকে কোনোরূপ সতর্কীকরণ তো দূরের কথা, কোনো আদেশ দেন নি বা নছীহতও করেন নি। বরং এখানে আল্লাহ্ তা‘আলা আহলে বাইত্ সম্পর্কে তাঁর দু’টি ফয়সালা বা সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। তা হচ্ছে, তিনি তাঁদের থেকে অপকৃষ্টতা অপসারিত করতে এবং তাঁদেরকে পরিপূর্ণরূপে পূতপবিত্র করতে চান। আর এ সিদ্ধান্ত ঘোষণার বাক্য শুরু করা হয়েছে انما (অবশ্যই) শব্দ দ্বারা। এর মানে হচ্ছে, এটি একটি অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত; কোনোরূপ দুই সম্ভাবনাযুক্ত বিকল্প সিদ্ধান্ত নয়। এ থেকে আহলে বাইতের পাপমুক্ততা (عصمة)-ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।
কিন্তু এর বাইরে কোরআন মজীদে কোথাওই হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর বিবিগণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই পাপমুক্ততা (عصمة)-এর ঘোষণা দেয়া হয় নি।
[এখানে আমরা বলে রাখতে চাই যে, কারো মা‘ছূম্ (معصوم পাপমুক্ত) হওয়ার মানে এই যে, তিনি নিশ্চিতভাবেই পাপমুক্ত ছিলেন, কিন্তু কারো মা‘ছূম্ না হওয়ার মানে এই নয় যে, তিনি নিশ্চিতভাবেই পাপ করেছেন। বরং মা‘ছূম না হওয়ার মানে হচ্ছে, পাপ থেকে মুক্ত থাকার নিশ্চয়তা না থাকা। এমতাবস্থায় কারো পাপে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে পাপী বলে গণ্য করা চলে না।]
কোরআন মজীদের উপরোদ্ধৃত আয়াত সমূহে ব্যবহৃত বাচনভঙ্গি থেকেই সুস্পষ্ট যে, হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর বিবিগণ মা‘ছূম ছিলেন না। অবশ্য কোরআন মজীদে তাঁদেরকে মু’মিনদের মাতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে (সূরাহ্ আল্-আহযাবঃ ৬) এবং হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর তাঁদের কাউকে বিবাহ করা মু’মিনদের জন্য হারাম করে দেয়া হয় (সূরাহ্ আল্-আহযাব ঃ ৫৩)। এ কারণে তাঁদের সাথে মু’মিনদের যে সম্মানার্হ সম্পর্ক তার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে তাঁদের মর্যাদাকে পাপমুক্ততার পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা করেন।
কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো মু’মিনদের জন্য মাতৃস্বরূপ হওয়া আর মা‘ছূম হওয়ার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই, ঠিক যেমন কোনো মু’মিন ব্যক্তির জন্মদাত্রী মায়ের সাথে তার সম্মানার্হ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তার মাকে অনিবার্যভাবেই মা‘ছূম বলে গণ্য করা সঠিক হতে পারে না। এমনকি কোনো মু’মিন ব্যক্তির পিতা-মাতা যদি কাফেরও হয় তাহলেও তাদের সাথে সম্মানার্হ ও সৌজন্যমূলক আচরণ অব্যাহত রাখার জন্য কোরআন মজীদে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু ঐ মু’মিন ব্যক্তির এ আচরণ তার পিতা-মাতাকে মু’মিনে পরিণত করবে না।
মু’মিনদের জন্য হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর বিবিগণকে মায়ের ন্যায় সম্মানার্হ গণ্য করার বিষয়টিও একই ধরনের। প্রকৃত পক্ষে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর স্ত্রীর মর্যাদাই তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে মু’মিনদের জন্য অপরিহার্য করেছে। কারণ, হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) মু’মিনদের জন্য পিতৃতুল্য, বরং পিতার চেয়ে অধিকতর সম্মান, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা পাবার হকদার। এমতাবস্থায় তাঁর পরে তাঁর কোনো স্ত্রীকে বিবাহ করলে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি পূর্বানুরূপ সম্মান, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা বজায় থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় তাঁর পরে তাঁর বিবিগণকে বিবাহ করা হারাম হওয়া ও তাঁদেরকে মাতৃতুল্য গণ্য করা অপরিহার্য ছিলো। কিন্তু এর দ্বারা কিছুতেই তাঁদেরকে মা‘ছূম বলে গণ্য করা চলে না।
যদিও অনুরূপ ক্ষেত্রে অতীতের নবী-রাসূলগণের (আঃ) বিবিগণের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা‘আলার বিধান কী ছিলো তা কোরআন মজীদে উল্লেখ করা হয় নি (এবং তা উল্লেখের প্রয়োজনও ছিলো না)। তবে আমরা নিদ্বির্ধায় ধরে নিতে পারি যে, অতীতের নবী-রাসূলগণের (আঃ) বিবিগণের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা‘আলার বিধান অভিন্ন ছিলো। কিন্তু তাঁদের ক্ষেত্রেও মা‘ছূম হওয়ার বিষয় প্রমাণিত হয় না। অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মা‘ছূম থেকে থাকলে তা ব্যক্তি হিসেবে, নবী-রাসূলের (আঃ) স্ত্রী হিসেবে নয়। তার প্রমাণ, কোরআন মজীদে হযরত নূহ্ (আঃ) ও হযরত লূত্ব (আঃ)-এর স্ত্রীর কুফরী ও জাহান্নামী হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে। একটি ঐশী মূলনীতি হিসেবে নবী-রাসূলের (আঃ) স্ত্রী তথা মু’মিনদের মাতা হওয়া যদি কারো পাপমুক্ততা নিশ্চিত করতো তাহলে ঐ দু’জন নারী তার ব্যতিক্রম হতো না।
নীতিগতভাবে তথা একটি ঐশী মূলনীতি হিসেবে উম্মাহাতুল মু’মিনীন অর্থাৎ হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর বিবিগণ-এর মা‘ছূম না হওয়ার তথা আহলে বাইত্-এর অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার বিষয়টি উল্লিখিত আয়াত সমূহ ও উপরোক্ত আলোচনা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। কোরআন মজীদের আরো কতক আয়াত থেকে এ বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ এখানে যা এজমালীভাবে প্রমাণিত হয় অন্য কতক আয়াত থেকে তা দৃষ্টান্ত সহকারে প্রমাণিত হয়।
কোরআন মজীদের সূরাহ্ আত্-তাহ্রীম্ থেকে জানা যায় যে, হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) তাঁর কোনো একজন স্ত্রীর কাছে একটি গোপন কথা বললে তিনি গোপনীয়তা ভঙ্গ করে তা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অপর এক স্ত্রীর কাছে বলে দেন। এছাড়া তাঁর দুই স্ত্রী [যথাসম্ভব ঐ দু’জনই অর্থাৎ যারা একজন আরেক জনের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর গোপন কথা বলে দিয়েছিলেন] “রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে” পরস্পরকে সাহায্য করতে তথা তাঁর বিরুদ্ধে কোনো একটি বিষয়ে চক্রান্ত করতে যাচ্ছিলেন। এ জন্য আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁদেরকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন ও সতর্ক করে দেন এবং তাওবাহ্ করার জন্য নছীহত্ করেন।[ আহলে সুন্নাতের ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য বলে পরিগণিত বিভিন্ন হাদীছ-গ্রন্থ ও তাফসীরে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর এ দু’জন স্ত্রীর নাম সুনির্দিষ্টভাবে এবং সংশ্লিষ্ট গোপন কথা সংক্রান্ত ঘটনা ও চক্রান্তের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লিখত আছে। কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে সুনির্দিষ্টভাবে তাঁদেরকে চিহ্নিত করা আমাদের অত্র আলোচনার জন্য অপরিহার্য নয়। বরং আমাদের আলোচনা হচ্ছে একটি নীতিগত আলোচনা। এ কারণে, তাঁদের মধ্য থেকে একজনের ব্যাপারেও যদি মা‘ছূম্ না হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয় (তা যিনিই হোন না কেন) তাহলে তা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, কেবল হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর স্ত্রীর মর্যাদা কাউকে মা‘ছূম বানাতে পারে না।]
এরশাদ হয়েছে ঃ
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ
“আর নবী যখন তাঁর স্ত্রীদের কারো কাছে কোনো একটি কথা গোপনে বললেন, অতঃপর সে (অন্য কাউকে) তা জানিয়ে দিলো এবং আল্লাহ্ তাঁর [রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর] কাছে তা প্রকাশ করে দিলেন তখন তিনি (তাঁর ঐ স্ত্রীকে) তার কিছুটা জানালেন এবং কিছুটা জানালেন না। আর তিনি যখন তাকে তা জানালেন তখন সে বললো ঃ কে আপনাকে এটি জানিয়েছে? তিনি বললেন ঃ পরম জ্ঞানী সর্বজ্ঞ (আল্লাহ্)ই আমাকে জানিয়েছেন।” (সূরাহ্আত-তাহরীম-৩)
এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, যে কোনো ঈমানদার কর্তৃক, বিশেষ করে নবীর (সাঃ) একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি কর্তৃক যাকে তিনি বিশ্বাস করে কোনো গোপন কথা বলেছিলেন Ñ তাঁর গোপন কথা অন্যের কাছে বলে দেয়া একটি গুরুতর বিষয় ছিলো। কিন্তু এখানেই শেষ নয়।
আল্লাহ্ তা‘আলা এরপর এরশাদ করেছেন ঃ
إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ
“তেমাদের দু’জনের অন্তর অন্যায়ের প্রতি ঝুঁকে পড়ার কারণে তোমরা যদি তাওবাহ্ করো (তো ভালো কথা), নচেৎ তোমরা দু’জন যদি তাঁর (রাসূলের) বিরুদ্ধে পরস্পরকে সহায়তা করো (তথা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করো) তাহলে (জেনে রেখো,) অবশ্যই আল্লাহ্ই তাঁর অভিভাবক, আর এছাড়াও জিবরাঈল, উপযুক্ত মু’মিনগণ ও ফেরেশতাগণ তাঁর সাহায্যকারী।” (সূরাহ্ আত্-তাহ্রীম ঃ ৪)
পরবর্তী আয়াত থেকে মনে হয় যে, তাঁদের দু’জনের কাজটি এমনই গুরুতর ছিলো যে কারণে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে তালাক প্রদান করা হলেও অস্বাভাবিক হতো না। আর তাতে দ্বিবচনের পরিবর্তে স্ত্রীবাচক বহুবচন ব্যবহার থেকে মনে হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে যারা এ চক্রান্তে অংশ নেন নি সম্ভবতঃ তাঁরাও বিষয়টি জানার পরে তাতে বাধা দেন নি বা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সাথে সাথে অবগত করেন নি, তাই এ শৈথিল্যের কারণে তাঁদেরকেও তালাক দেয়া হলে তা-ও অস্বাভাবিক হতো না।
এরশাদ হয়েছে ঃ
عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا
“তিনি (রাসূল) যদি তোমাদেরকে তালাক্ব প্রদান করেন তাহলে হয়তো তাঁর রব তোমাদের পরিবর্তে তাঁকে তোমাদের চেয়ে উত্তম অকুমারী ও কুমারী স্ত্রীবর্গ প্রদান করবেন যারা হবে ঈমানদার, (আল্লাহর কাছে) আত্মসমর্পিত, আজ্ঞাবহ, তাওবাহ্কারিনী, ‘ইবাদত-কারিনী ও রোযা পালনকারিনী (বা আল্লাহর পথে পরিভ্রমণকারিনী)।” (সূরাহ্ আত্-তাহ্রীম ঃ ৫)
এ আয়াতে এ ধরনের ইঙ্গিতও রয়েছে যে, হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ঐ সময় জীবিত বিবিগণের কারো মধ্যেই এতে উল্লিখিত সবগুলো গুণ-বৈশিষ্ট্য বাঞ্ছিত সর্বোচ্চ মাত্রায় ছিলো না।
এ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর বিবিগণ মা‘ছূম ছিলেন না এবং তাঁরা আহলে বাইত্-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। কিন্তু এরপরও অনেকে ভাবাবেগের বশে কেবল আল্লাহর রাসূলের স্ত্রী হবার কারণে তাঁদেরকে পাপ ও ভুলের উর্ধে গণ্য করেন। তাঁদের এ ভুল ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য কোরআন মজীদের নিুোক্ত আয়াতই যথেষ্ট হওয়া উচিত যা হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর স্ত্রীগণের সমালোচনা ও তাঁদের উদ্দেশে উচ্চারিত হুমকির ধারাবাহিকতায় তাঁদেরকে সতর্ক করার লক্ষ্যে নাযিল হয়েছে ঃ
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ
“যারা কাফের হয়েছে তাদের জন্য আল্লাহ্ নূহের স্ত্রী ও লূত্বের স্ত্রীর উপমা প্রদান করেছেন; তারা দু’জন আমার দু’জন নেক বান্দাহর আওতায় (বিবাহাধীনে) ছিলো, কিন্তু তারা উভয়ই তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। ফলে তারা দু’জন (নূহ্ ও লূত্ব) তাদের দু’জনকে আল্লাহর (শাস্তি) থেকে রক্ষা করতে পারলো না; আর তাদেরকে বলা হলো ঃ (অন্যান্য) প্রবেশকারীদের সাথে দোযখে প্রবেশ করো।” (সূরাহ্ আত্-তাহ্রীম্ ঃ ১০)
আহলে বাইত্ কারা?
আমরা ভূমিকায় যেমন উল্লেখ করেছি, হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর যুগ থেকে শুরু করে এ ব্যাপারে যে সর্বসম্মত মত (ইজ্মা‘) চলে এসেছে তা হচ্ছে, কোরআন মজীদে আহলে বাইত্ বলতে হযরত ফাতেমাহ্, হযরত আলী, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসেন (রাযীয়াল্লাাহু তা‘আালাা ‘আন্হুম্ আজ্মা‘ঈন্)-কে বুঝানো হয়েছে তেমনি আালে মুহাম্মাদ (সাঃ) বলতেও তাঁদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ বিষয়ের সমর্থনে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত প্রচুর হাদীছ রয়েছে।
বর্ণনাসূত্রের বিচারে এ বিষয়ক হাদীছগুলো মুতাওয়াতির কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনায় না গিয়েও আমরা বলতে পারি যে, প্রথমতঃ এ সব হাদীছের বিষয়বস্তু ইসলামের চারটি অকাট্য জ্ঞানসূত্রের কোনোটির সাথেই সাংঘর্ষিক নয় এবং দ্বিতীয়তঃ সংশ্লিষ্ট আয়াত নাযিলকালে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর পুত্রসন্তান না থাকা ও কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে তাঁর বিবিগণ মা‘ছূম না হওয়া তথা আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ক হাদীছগুলো গ্রহণ করা ছাড়া সংশ্লিষ্ট আয়াতাংশের প্রায়োগিকতা থাকে না। কারণ, সে ক্ষেত্রে আদৌ তাঁর কোনো আহলে বাইত্ থাকে না এবং সংশ্লিষ্ট আয়াতাংশ অর্থহীন হয়ে যায় Ñ যে ধরনের উক্তি থেকে চির জ্ঞানময় সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ্ তা‘আলা পরম প্রমুক্ত।
অধিকন্তু আয়াতে মুবাাহালাহ্ (সূরাহ্ আালে ‘ইমরান্ ঃ ৬১) অনুযায়ী হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) যে আমল করেন তদ্সংক্রান্ত যে তথ্যের ওপরে উম্মাহর মধ্যে ইজ্মা‘ রয়েছে তা থেকেও উক্ত চারজন মহান ব্যক্তিত্বের আহলে বাইত্ বা আালে মুহাম্মাদ (সাঃ) হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য সমর্থন পাওয়া যায়।
নাজরানের খৃস্টান ধর্মনেতাদের কাছে ইসলামের সত্য দ্বীন ও হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সত্যিকারের পয়গাম্বর হওয়ার বিষয়টি অকাট্যভাবে সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা ইসলাম ও হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর বিরোধিতার ব্যাপারে, বিশেষ করে হযরত ‘ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে একগুঁয়েমি করতে থাকলে আল্লাহ্ তা‘আলা তাদেরকে লা‘নতের চ্যালেঞ্জ দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)কে নির্দেশ দেন; এরশাদ করেন ঃ
فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ
“(হে রাসূল!) আপনার কাছে প্রকৃত জ্ঞান এসে যাওয়ার পরেও যে আপনার সাথে এ ব্যাপারে (‘ঈসার ব্যাপারে) বিতর্ক করে তাকে বলুন ঃ এসো আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমাদের পুত্রদেরকে, আমাদের নারীদেরকে ও তোমাদের নারীদেরকে এবং আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে, অতঃপর আমরা প্রার্থনা করি এবং মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর লা‘নত করি।” (সূরাহ্ আালে ‘ইমরাান্ ঃ ৬১)
ইসলামের সকল মাযহাব ও ফির্ক্বাহ্র সূত্রে বর্ণিত হাদীছ সমূহের ভিত্তিতে সমগ্র উম্মাহ্র কাছে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত তথ্য অনুযায়ী হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত ফাতেমাহ্, হযরত আলী, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসেন (রাযীয়াল্লাহু তা‘আালা ‘আন্হুম্ আজ্মা‘ঈন্)-কে স্বীয় চাদর বা ‘আবা-র নীচে নিয়ে নাজ্রানের খৃস্টানদের সাথে মুবাাহালাহ্ করতে যান এবং এ সময় আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে যে দো‘আ করেন তাতে তাঁদেরকে “এরাই আমার আহলে বাইত্” বলে উল্লেখ করেন। এ সংক্রান্ত হাদীছগুলোরও বিষয়বস্তু এমন যা ইসলামের অকাট্য জ্ঞানসূত্র সমূহের কোনোটির সাথেই সাংঘর্ষিক নয় এবং এ ব্যাপারে এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো বর্ণনা নেই। এমতাবস্থায় এটিকে গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। নচেৎ ধরে নিতে হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ আয়াত অনুযায়ী আমল করেন নি Ñ যে ধারণা নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যানযোগ্য।
লক্ষণীয় যে, সংশ্লিষ্ট আয়াত অনুযায়ী হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর জন্য তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষগুলোকে নিয়ে মুবাাহালাহ্ করতে যাওয়া অপরিহার্য ছিলো। এ আয়াতে উভয় পক্ষে মুবাাহালায় অংশগ্রহণকারীকে তিন ধরনের লোকদেরকে নিয়ে এতে অংশগ্রহণ করতে বলা হয়, তা হচ্ছে ঃ انفسنا (আমরা নিজেরা), ابنئنا (আমাদের পুত্রগণ/ বংশধর পুরুষগণ) ও نسائنا (আমাদের নারীগণ/ স্ত্রী-কন্যাগণ)। এ আয়াতে প্রদত্ত নির্দেশের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যাদেরকে নিয়ে মুবাাহালাহ্ করতে গেলেন সুস্পষ্ট যে, তাঁদের মধ্য থেকে হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ)কে ابنئنا (আমাদের পুত্রগণ/ পুরুষ বংশধরগণ) হিসেবে, হযরত ফাতেমাহ্ (রাঃ)কে نسائنا (আমাদের নারীগণ অর্থাৎ প্রিয়তম নারীগণ) ও হযরত আলী (রাঃ)কে انفسنا (আমরা নিজেরা) হিসেবে সাথে নিয়ে যান। অর্থাৎ তিনি তাঁর পুরো আহলে বাইত্কে সাথে নিয়ে যান।
এখানে আরো গভীরভাবে তলিয়ে চিন্তা করার বিষয় হচ্ছে এই যে, মুবাাহালাহ্র আয়াতে যাদেরকে সাথে নিয়ে মুবাাহালাহ্ করার নির্দেশ দেয়া হয় তাঁদের সম্পর্কে আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা হলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্য কন্যাকে নয়, বরং তাঁর স্ত্রীগণকে সাথে নিতে হতো, অথবা কন্যার সাথে সাথে স্ত্রীগণকেও সাথে নিতে হতো। অবশ্য জীবিত পুত্রসন্তান না থাকা অবস্থায় নাতিদ্বয়কে নিয়ে যাওয়ার যৌক্তিকতা থাকলেও আভিধানিক তাৎপর্যের দৃষ্টিতে জামাতাকে সাথে নেয়ার বিষয়টি এর আওতায় আসে না। কিন্তু যেহেতু মুবাাহালাহ্র ক্ষেত্রে রক্ত বা বৈবাহিক সম্পর্কের নিকটতম ব্যক্তিদেরকে সাথে নেয়ার যৌক্তিকতা ছিলো না এবং প্রতিপক্ষও তা দাবী করতো না, বরং দু’টি আদর্শিক পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নেতার জন্য আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে যারা তাঁর নিকটতম ও পরবর্তী উত্তরাধিকারী তথা নেতার সাথে যারা ধ্বংস হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট আদর্শের চিরবিলুপ্তি ঘটবে তাঁদেরকে সাথে নিয়েই মুবাাহালাহ্ করা অপরিহার্য ছিলো।
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ইসলামের সকল মত-পথের সূত্রে বর্ণিত হাদীছ-ভিত্তিক সর্বসম্মত মত অনুযায়ী হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে তাঁর সম্পর্ককে হযরত মূসা ও হযরত হারূন (আঃ)-এর সম্পর্কের অনুরূপ বলে উল্লেখ করেছেন। এর মানে হচ্ছে, হযরত হারূন (আঃ) যেরূপ হযরত মূসা (আঃ)-এর আদর্শিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন, ঠিক সেভাবেই হযরত আলী (রাঃ) হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর আদর্শিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁকে সাথে নিয়ে না গেলে মুবাহালাহ্ অসম্পূর্ণ থাকতো। সম্ভবতঃ প্রতিপক্ষও এ বিষয়টি অবগত ছিলো এবং এ কারণে তাঁকে সাথে নিয়ে না গেলে তা প্রতিপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য হতো না।
অনুরূপভাবে বুঝা যায়, হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) জানতেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকে “আমাদের নারীগণ” হিসেবে তথা আহলে বাইতের নারী সদস্য হিসেবে সাথে না নেয়ায় প্রতিপক্ষের কাছ থেকে প্রতিবাদের আশঙ্কা ছিলো না অর্থাৎ প্রতিপক্ষও জানতো যে, তাঁর স্ত্রীগণ আদর্শিক-পারিভাষিক দিক থেকে তাঁর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।
এ থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, পারিভাষিক অর্থে কোনো নবী বা রাসূলের আহলে বাইত্ বা আালে রাসূলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য অভিধানিক অর্থে পরিবারের সদস্য বা বংশধর হওয়া অপরিহার্য নয়, বরং এর বাইরে থেকেও অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। অর্থাৎ পারিভাষিক অর্থে একজন নবী বা রাসূলের আহলে বাইত্ বা আালে রাসূলের অন্তর্ভুক্ত তাঁরাই যারা তাঁর আদর্শিক সত্তার অংশ এবং তাঁর আদর্শিক উত্তরাধিকারী। হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারূন (আঃ) এবং হযরত মূসা ও হযরত ইউশা‘ বিন্ নূন্ (আঃ)-এর মধ্যে যে সম্পর্ক ছিলো তা এ ধরনেরই এবং এ কারণেই হযরত ইউশা‘ বিন্ নূন্ (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)-এর পুত্র না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর আদর্শিক নেতৃত্বের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। একই কারণে হযরত আলী (রাঃ) হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর পুত্র না হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আহলে বাইত্-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
ইসলামে আহলে বাইত্-এর মর্যাদা
কোরআন মজীদে ও বিভিন্ন হাদীছে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর আহলে বাইত্-এর দ্বীনী মর্যাদা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু উল্লেখ রয়েছে। বিশেষ করে কোরআন মজীদের যে সব আয়াতে এ সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ইখলাছের সাথে ও নিরপেক্ষভাবে অর্থগ্রহণ ও ব্যাখ্যা করা হলে সে সব আয়াত থেকেও হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর আহলে বাইত্-এর বিশেষ দ্বীনী মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। তেমনি বিভিন্ন মুতাওয়াতির হাদীছেও এ সম্বন্ধে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এখানে আমরা কেবল সেই সব দলীলেরই আশ্রয় নেবো যার তাৎপর্যের ব্যাপারে দ্বিমতের অবকাশ নেই।
এ পর্যায়ে প্রথমেই আমরা যা উল্লেখ করতে চাই তা হচ্ছে আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীন আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসাকে মু’মিনদের জন্য অপরিহার্য করেছেন; এরশাদ হয়েছে ঃ
قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى
(হে রাসূল!) বলুন, আমি এজন্য (আল্লাহর হেদায়াত পৌঁছে দেয়ার বিনিময়ে) তোমাদের কাছে আমার ঘনিষ্ঠতমদের জন্য ভালোবাসা ব্যতীত কোনো বিনিময় চাই না।” (সূরাহ্ আশ্-শূরা ঃ ২৩)
এ আয়াতে মু’মিনদের জন্য হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর স্বজনদের (قربی) প্রতি ভালোবাসাকে অপরিহার্য করা হয়েছে। কারণ, এ ব্যাপারে দ্বিমতের অবকাশ নেই যে, এতে স্বজন (قربی) বলতে তাঁর আহলে বাইত্কেই বুঝানো হয়েছে। আর এতে যদি ব্যাপকতর অর্থে তাঁর আত্মীয়-স্বজন বা বনি হাশেম্কে বুঝানো হয়ে থাকে তাহলেও তাঁদের মধ্যে আহলে বাইত্ অগ্রগণ্য।
ইসলামের সকল মাযহাব ও ফির্ক্বাহর সূত্রে হযরত ফাতেমাহ্ যাহরা’, হযরত আলী, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসেন (রাযীয়াল্লাহু তা‘আালা ‘আন্হুম্ আজ্মা‘ঈন্)-এর মর্যাদা সম্পর্কে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যার বিষয়বস্তুসমূহ মুতাওয়াতির পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। অবশ্য তা সত্ত্বেও কেউ হয়তো সে সবের তাওয়ার্তুর সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারেন, কিন্তু এ সবের মধ্যে এমন কতগুলো বিষয় রয়েছে যা বিতর্কের উর্ধে এবং যে সব ব্যাপারে সকলেই একমত। এ সব বিতর্কাতীত বিষয়ের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই যে, হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর উম্মাতের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন সর্বাধিক জ্ঞানী।
রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ
انا مدينة العلم و علی بابها.
“আমি জ্ঞানের নগরী, আর আলী তার দরযা।”
এর মানে হচ্ছে, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ও পুরোপুরি নির্ভুল জ্ঞান কেবল হযরত আলী (রাঃ)-এর কাছেই ছিলো এবং ইসলামের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান পেতে হলে তাঁর দ্বারস্থ হওয়া অপরিহার্য।
অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে ইজ্মা‘ রয়েছে এবং এ কারণে জুম‘আহ্ নামাযের খোত্ববাহ্ সমূহে অপরিহার্যভাবে উল্লেখ করা হয় যে, হযরত ফাতেমাহ্ (রাঃ) বেহেশতে নারীদের নেত্রী (سيدة نساء اهل الجنة) এবং হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ) বেহেশতে যুবকদের নেতা (سيدا شباب اهل الجنة)।
এ হচ্ছে এমন মর্যাদা যা হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর কোনো বিবি বা অন্য কোনো ছাহাবীর জন্য বর্ণিত হয় নি।
অন্যদিকে, অত্র পুস্তকের ভূমিকায় যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, যে কোনো নামাযের শেষ রাক্‘আতে বসা অবস্থায় হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সাথে তাঁর আহলে বাইত্-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ অপরিহার্য, নচেৎ নামায ছহীহ্ হবে না। বিশেষ করে হানাফী মায্হাবের অনুসারীরা এ দরূদটি এভাবে পড়ে থাকেন ঃ
اللهم صلِّ علی محمد و علی آل محمد کما صلَّيت علی ابراهيم و علی آل ابراهيم؛ انک حميد مجيد. اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهيم و علی آل ابراهيم؛ انک حميد مجيد.
“হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ ও আালে মুহাম্মাদের প্রতি ছালাত্ করো ঠিক যেভাবে ছালাত্ করেছো ইবরাহীম ও আালে ইবরাহীমের প্রতি; অবশ্যই তুমি পরম প্রশংসিত পরম বরকতময়। হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ ও আালে মুহাম্মাদের প্রতি বরকত নাযিল করো ঠিক যেভাবে বরকত নাযিল করেছো ইবরাহীম ও আালে ইবরাহীমের প্রতি; অবশ্যই তুমি পরম প্রশংসিত পরম বরকতময়।”
এ দরূদের মধ্যে বিরাট চিন্তার খোরাক রয়েছে। তা হচ্ছে, হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর প্রতি ছালাত্ করা ও বরকত নাযিলের জন্য আবেদনের সাথে সাথে তাঁর আহলে বাইত্-এর প্রতি কেবল ছালাত্ করা ও বরকত নাযিলের আবেদনই করা হয় নি, বরং হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর প্রতি ঠিক সেভাবে ছালাত্ করা ও বরকত নাযিলের জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে আবেদন করা হয়েছে যেভাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে ছালাত্ করা ও বরকত নাযিল করা হয়েছিলো। অন্যদিকে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর আহলে বাইত্-এর প্রতি ঠিক সেভাবে ছালাত্ করা ও বরকত নাযিলের জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে আবেদন জানানো হয়েছে যেভাবে আালে ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে ছ¡ালাত্ করা ও বরকত নাযিল করা হয়েছিলো। এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর আহলে বাইত্কে আালে ইবরাহীমের (আঃ)-এর সমপর্যায়ের গণ্য করা হয়েছে।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আালে ইবরাহীম (আঃ) কা’রা ছিলেন?
এখানে “আালে ইবরাহীম” কথাটি যে আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নি, বরং পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে ব্যাপারে বিতর্কের কোনোই অবকাশ নেই। কারণ, এখানে “আালে ইবরাহীম” বলতে নিঃশর্তভাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পরিবার, বা সন্তানগণ বা বংশধরগণকে বুঝানো হয় নি। কারণ, তাঁর বংশধরগণের মধ্যকার নাফরমানদেরকে মুসলমানদের নামায-মধ্যস্থ দরূদে শরীক করা হবে এ প্রশ্নই ওঠে না।
আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীন নিজের পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে মানব জাতির জন্য ইমাম বা নেতা মনোনীত করণ সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
আর ইবরাহীমকে যখন তার রব কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করলেন এবং সে তা (সাফল্যের সাথে) সমাপ্ত করলো (তাতে উত্তীর্ণ হলো) তখন তিনি (তার রব/ আল্লাহ্) বললেন ঃ অবশ্যই আমি তোমাকে মানব জাতির জন্য নেতা (ইমাম) মনোনীতকারী।” (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ ঃ ১২৪)
তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন ঃ
وَمِن ذُرِّيَّتِي
“আর আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও কি (ইমাম নিয়োগ করা হবে)?” (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ ঃ ১২৪)
জবাবে আল্লাহ্ তা‘আলা বললেন ঃ
لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
“(হ্যা, অবশ্যই নিয়োগ করবো, তবে) আমার এ অঙ্গীকার যালেমদের জন্য নয়।” (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ ঃ ১২৪)
এ থেকে সুস্পষ্ট যে, এখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে ‘পরিপূর্ণ নেককার’দের ব্যাপারে এ অঙ্গীকার করা হয়েছে। আর আমরা জানি যে, তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকে বহু নবী-রাসূলের (আঃ) আবির্ভাব হয়েছিলো এবং তাঁরা নিজ নিজ যুগে দ্বীনী নেতৃত্বের (ইমাতের) অধিকারী ছিলেন। অতএব, এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আমরা নামাযে যে দরূদ পাঠ করি তাতে যে “আালে ইবরাহীম”-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার দ্বারা মূলতঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশে আগত নবী-রাসূলগণ (আঃ)কে বুঝানো হয়েছে। আর আালে মুহাম্মাদের (সাঃ) প্রতি আালে ইবরাহীমের অনুরূপ দরূদ করার মাধ্যমে তাঁদের জন্য আালে ইবরাহীমের ‘সমতুল্য’ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আালে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর তথা হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর আহলে বাইত্-এর সদস্যগণ নবী-রাসূল না হলেও তাঁদের মর্যাদা আালে ইবরাহীমের তথা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশে আগত নবী-রাসূলগণের (আঃ) সমতুল্য।
এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে, আালে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর তথা হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর আহলে বাইত্-এর সদস্যগণ যখন নবী-রাসূল নন তখন কীভাবে ও কী কারণে তাঁদের মর্যাদা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশে আগত নবী-রাসূলগণ (আঃ)-এর মর্যাদার সমতুল্য হতে পারে?
এ প্রশ্নের জবাব আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে নেতা বা ইমাম নিয়োগ এবং এরপর পরবর্তী নেতা বা ইমামগণ সম্বন্ধে তাঁর প্রশ্ন ও আল্লাহ্ তা‘আলার জবাবের মধ্যে নিহিত রয়েছে।
আমরা সাধারণতঃ দ্বীনী মর্যাদার ক্ষেত্রে নবী-রাসূলের মর্যাদাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা বলে মনে করে থাকি। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে ইমাম নিয়োগের ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের সর্বোচ্চ মর্যাদা হচ্ছে “আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে মনোনীত” নেতা বা ইমামের মর্যাদা। কারণ, হযরত ইবরাহীম (আঃ) দীর্ঘ বহু বছর যাবত রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেন এবং বহু কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; কেবল এর পরেই আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁকে নেতা বা ইমাম মনোনীত করেন। অতএব, এতে সন্দেহ নেই যে, “আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে মনোনীত” নেতা বা ইমামের মর্যাদা তাঁর পক্ষ থেকে মনোনীত নবী বা রাসূলের মর্যাদার ওপরে।[ এখানে আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, এ মর্যাদা কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ইমামের; কোনো পার্থিব নেতৃত্বের জন্য নয়, এমনকি মুসলিম জনগণের দ্বারা নির্বাচিত কোনো দ্বীনী নেতার জন্য এ মর্যাদা নয়, তা সে নেতা মুসলিম জনগণের সর্বসম্মতিক্রমেই নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হোন না কেন।]তাই হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) সহ খুব কম সংখ্যক রাসূলই (আঃ) আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে ইমাম মনোনীত হয়েছিলেন।
আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নেককার বংশধরদেরকে ইমামত প্রদানের যে প্রতিশ্র“তি দেন তদনুযায়ী হযরত ইস্হাক্ব ও হযরত ইয়া‘কূব্ (আঃ) সহ অনেককে ইমামত প্রদান করেন। এরশাদ হয়েছে ঃ
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ73وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ
“আর আমি তাকে (ইবরাহীমকে) দান করলাম ইস্হাক্বকে ও অতিরিক্ত (দান করলাম) ইয়াকূবকে এবং (তাদের) প্রত্যেককেই সৎকর্মশীল বানিয়েছি। আর তাদেরকে ইমাম বানিয়েছি যারা আমার আদেশে লোকদেরকে পরিচালিত করতো এবং তাদেরকে উত্তম কর্ম সম্পাদন, নামায ক্বায়েম রাখা ও যাকাত প্রদানের বিষয়ে ওয়াহী করেছি, আর তারা ছিলো আমার ‘ইবাদতকারী (অনুগত বান্দাহ্)। (সূরাহ্ আল্-আম্বিয়া’ ঃ ৭২-৭৩)
উপরোদ্ধৃত আয়াত দু’টির মধ্যে প্রথম আয়াতে দু’জন নবীর কথা বলা হলেও দ্বিতীয় আয়াতে ইমাম বানানো প্রসঙ্গে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে, দ্বিবচন নয়। এ থেকে প্রমাণিত যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে কেবল উপরোক্ত দু’জন নবী (আঃ)ই ইমাম মনোনীত হন নি, বরং দু’জন নবীর নামোল্লেখ ও অন্য ইমামগণের নামোল্লেখ না করার ফলে এ সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে যে, অন্য ইমামগণ নবী ছিলেন না, তবে নবী না হলেও তাঁরা ঐশী ইল্হাম্-এর [কোরআন মজীদে ইলহাম্ অর্থে “ওয়াহী” শব্দ ব্যবহারের একাধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে।]ভিত্তিতে লোকদেরকে পরিচালনা করতেন।
এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে নবী-রাসূল ও ইমাম মনোনয়নের উদ্দেশ্য বিনা কারণে কেবল তাঁর কতক বান্দাহ্কে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা নয়, বরং এ সব পদ হচ্ছে কতক দায়িত্ব পালনের পদ; দায়িত্বের প্রয়োজনে ব্যতীত আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে এ সব পদে কাউকে মনোনীতকরণ অকল্পনীয়। আর আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে মনোনীত নবী-রাসূলগণের (আঃ) দায়িত্ব ছিলো তাঁর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। অন্যদিকে আল্লাহর মনোনীত নেতা বা ইমামের দায়িত্ব ঐশী হেদায়াত অনুযায়ী আল্লাহর বান্দাহদেরকে সঠিক পথ দেখানো ও সে পথে পরিচালিত করা, আর যে সব নবী-রাসূল (আঃ) একই সাথে ইমাম বা নেতা ছিলেন তাঁরা আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়ার সাথে সাথে এ দায়িত্বও পালন করেছেন।
এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা‘আলার পূর্ণাঙ্গ বাণী (কোরআন মজীদ) নাযিল করা ও তা সংরক্ষিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করার পর আর আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে নতুন কোনো নবী বা রাসূল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা থাকে নি। কিন্তু আল্লাহ্ তা‘আলার বাণীর সঠিক তাৎপর্য গ্রহণ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তদনুযায়ী আল্লাহর বান্দাহ্দেরকে পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা একইভাবে থেকে যায়। আর বলা বাহুল্য যে, পাপমুক্ততা ও নির্ভুলতার নিশ্চয়তা বিহীন কোনো ব্যক্তির পক্ষে এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। অতএব, নবীর অবর্তমানে এ দায়িত্ব পালন করার জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে মনোনীত নিষ্পাপ ও ভুলমুক্ত নেতা বা ইমাম মনোনীত হওয়া অপরিহার্য। নচেৎ বান্দাহ্দের জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার হুজ্জাত্ পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়, ফলে বান্দাহ্ ইখলাছ¡ সহকারে সঠিক ফয়সালায় উপনীত হবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও ভ্রান্তিতে নিপতিত হলে সে জন্য পাকড়াও-এর উপযোগী হবে না। আরো এগিয়ে বলতে হয় যে, আল্লাহ্ তা‘আলা নবীর অবর্তমানে তাঁর বান্দাহ্দেরকে এরূপ একটি অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ফেলে রাখবেন তিনি এ ধরনের দুর্বলতা থেকে প্রমুক্ত।
এ প্রসঙ্গে আরো লক্ষণীয় বিষয় এই যে, নবী-রাসূল নন এমন ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে নেতা বা ইমাম নিয়োগের বিষয়টি যে কেবল হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ওফাতের পরেই প্রাসঙ্গিক হয়েছে, এর পূর্বে প্রাসঙ্গিক ছিলো না এমন কথাও নিশ্চিত করে বলা চলে না। বরং অতীতেও বিভিন্ন নবী-রাসূলের (আঃ) আবির্ভাবের মধ্যবর্তী অন্তর্বর্তী কালে আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে এ ধরনের নেতা বা ইমাম নিয়োগ করা হয়েছে তা পুরোপুরি সুনিশ্চিত। কারণ, আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীন বানী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে এরশাদ করেন ঃ
وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ
“আর আমি ইচ্ছা করি যে, ধরণীর বুকে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছে তাদের ওপর অনুগ্রহ করি এবং তাদেরকে নেতা (ইমাম) বানাই আর তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানাই।” (সূরাহ্ আল্-ক্বাছাছ¡ ঃ ৫)
এ আয়াতে যে কেবল এমন নেতার কথা বলা হয়েছে যারা একই সাথে নবী-রাসূল ছিলেন তা নয়। বরং বুঝা যায় যে, কোনো নবীর কাছে আগত হেদায়াত বিকৃত হওয়া ও নতুন করে হেদায়াত সহকারে নতুন নবীর আগমন ঘটার পূর্ববর্তী অন্তবর্তীকালে পূর্ববর্তী অবিকৃত হেদায়াত অনুযায়ী লোকদেরকে পরিচালনা করার জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে নবী-রাসূলের গুণাবলী সম্পন্ন বিভিন্ন নেতা বা ইমাম প্রেরণ করা হয়েছিলো এবং উক্ত আয়াতে তাঁদের কথাই বলা হয়েছে।
কোরআন মজীদের উক্ত দলীল সমূহ এবং নামাযে পঠিত দরূদের (যা ‘আমলের ক্ষেত্রে ইজ্মা প্রমাণ করে) বক্তব্যের আলোকে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ওফাতের পরে তাঁর আহলে বাইত্-এর আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ইমামতের ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ থাকে না। আর এ থেকে গাদীরে খুম্-এ হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) যে, হযরত আলী (রাঃ)কে উম্মাতের জন্য ‘মাওলা’ বলে পরিচিত করিয়ে দেন তাতে ‘মাওলা’ শব্দের তাৎপর্য যে ‘নেতা ও শাসক’ তথা তাঁর পরে তাঁর ‘খলীফাহ্’ এতেও সন্দেহের অবকাশ নেই।
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, গাদীরে খুম্ সংক্রান্ত হাদীছগুলো মূল বিষয়বস্তুর বিচারে সর্বোচ্চ পর্যায়ের তাওয়াতুরের অধিকারী। এ সব হাদীছ প্রতিটি স্তরে বিপুল সংখ্যক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এবং সকল মাযহাব ও ফির্ক্বাহ্র ধারাবাহিকতায় সংকলিত প্রায় সকল হাদীছ-গ্রন্থেই স্থানলাভ করেছে।
গাদীরে খুম্ সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীছের বর্ণনায় কতক বিষয়ে সামান্য বিভিন্নতা থাকলেও কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে কোনোই মতপার্থক্য নেই। সংক্ষেপে তা হচ্ছে, বিদায় হজ্বের পর হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) মক্কাহ্ ত্যাগ করে মদীনাহ্র উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে ১৮ই যিল্-হাজ্ব তারিখে মক্কাহ্র অদূরে গাদীরে খুম্ নামক স্থানে উপনীত হওয়ার পরে প্রচণ্ড গরম সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গীদেরকে যাত্রাবিরতি করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং যে সব ছাহাবী এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য লোক পাঠিয়ে দেন, আর যারা তখনো এসে পৌঁছেন নি তাঁদের আগমনের জন্য অপেক্ষা করেন। তাঁর নির্দেশে কতগুলো উটের হাওদার গদী একত্র করে একটি মঞ্চের মতো বানানো হয় এবং সকলে এসে পৌঁছলে তিনি হযরত আলী (রাঃ)কে সাথে নিয়ে সে মঞ্চে আরোহণ করেন। অতঃপর ভূমিকাস্বরূপ একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদানের পর তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর হাত উঁচু করে তুলে ধরে বলেন ঃ
من کنت مولاه فهذا علی مولاه.
“আমি যার মাওলা, অতঃপর এই আলী তার মাওলা।”
হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) যে গাদীরে খুমের সমাবেশে এ কথা বলেছিলেন এ ব্যাপারে কোনোই দ্বিমত নেই, কিন্তু এ কথার তাৎপর্য সম্পর্কে দ্বিমত করা হয়েছে। অনেকে এখানে “মাওলা” (مولی) শব্দের অর্থ করেছেন ‘বন্ধু’ ও ‘পৃষ্ঠপোষক’; এর অন্যতম অর্থ ‘শাসক’ হলেও তাঁরা তা গ্রহণ করেন নি। অবশ্য ব্যাপক অর্থবোধক এ শব্দটি কোরআন মজীদে ‘বন্ধু’ ও ‘পৃষ্ঠপোষক’ অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তিনটি কারণে এ ক্ষেত্রে তা গ্রহণীয় নয়।
প্রথমতঃ কোরআন মজীদে মু’মিনদেরকে পরস্পরের ‘বন্ধু’ ও ‘পৃষ্ঠপোষক’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে (সূরাহ্ আল্-মায়েদাহ্ ঃ ৫৫), ফলে স্বাভাবিকভাবেই হযরত আলী (রাঃ)ও মু’মিনদের ‘বন্ধু’ ও ‘পৃষ্ঠপোষক’। এমতাবস্থায় হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) কর্তৃক হযরত আলী (রাঃ)কে মু’মিনদের ‘বন্ধু’ ও ‘পৃষ্ঠপোষক’ হিসেবে আলাদাভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কোনো মানে হয় না। আর বলা বাহুল্য যে, তিনি কোনো অর্থহীন কাজ করতে পারেন না।
দ্বিতীয়তঃ, কেউ কেউ যেমন দাবী করেন যে, হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ছাহাবীর শা’নে উৎসাহব্যঞ্জক ও প্রশংসাসূচক কথা বলতেন এবং হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে তাঁর এ উক্তিটিও তদ্র প। যদিও যথার্থতা ছাড়া কেবল উৎসাহ প্রদানের জন্য কোনো ভিত্তিহীন কথা বলা বা ভিত্তিহীন প্রশংসা করার মতো অভ্যাস থেকে নবী-রাসূলগণ (আঃ) মুক্ত ছিলেন, তথাপি যুক্তির খাতিরে তা সম্ভব মনে করলেও এ জন্য প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ছাহাবীদেরকে সেখানে অপেক্ষা করতে বাধ্য করা সহ যে আনুষ্ঠানিকতার আশ্রয় নেয়া হয়েছিলো এরূপ একটি মামূলী বিষয়ের জন্য তার আশ্রয় নেয়া এক ধরনের রসিকতার শামিল আল্লাহর মনোনীত যে কোনো নবী-রাসূলই (আঃ) যা থেকে মুক্ত।
তৃতীয়তঃ বিচারবুদ্ধি (‘আক্বল্)-এর দাবী অনুযায়ী নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা ও ওয়াহী নাযিল সমাপ্ত হওয়ার পরে মওজূদ ওয়াহীর সঠিক ব্যাখ্যা ও উম্মাতের পরিচালনার জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে নিষ্পাপ ও নির্ভুল ইমাম মনোনীত হওয়া প্রয়োজন অথচ অন্য কাউকে এ দায়িত্বের জন্য মনোনীত করা হয় নি, এমতাবস্থায় গাদীরে খুমে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর এ উক্তিতে উল্লিখিত “মাওলা” (مولی) শব্দ থেকে ‘শাসক’ অর্থ গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নেই।
এবার আমরা বিষয়টিকে ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থাৎ বাস্তবতার আলোকে দেখতে চাই। তা হচ্ছে, আমরা যদি ধরে নেই যে, নবুওয়াত্ ও রিসালাতের ধারাবাহিকতা সমাপ্তির পরে মুসলমানদের নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্বের জন্য আল্লাহ্ তা‘আলা কাউকে মনোনীত করে দেন নি, বরং বিষয়টিকে মুসলিম উম্মাহ্র নির্বাচনের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন সে ক্ষেত্রে উম্মাহর জন্য কী ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অপরিহার্য?
যেহেতু বিষয়টি কোনো আদর্শনিরপেক্ষ নিরেট পার্থিব বিষয়ের (যেমন ঃ রাস্তাঘাট নির্মাণ, বাজার বা কারখানা পরিচালনা, গৃহের ডিজাইন করা ইত্যাদির) সাথে জড়িত নয়, বরং দ্বীন ও শরী‘আহর বাস্তবায়নের সাথে জড়িত সেহেতু ইখ্লাছের দাবী হচ্ছে এই যে, দ্বীনী দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির ওপরে এ দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হয় নি।
দ্বীনী নেতৃত্বের জন্য সাধারণভাবে যে গুণাবলী অপরিহার্য এবং যে গুণাবলীর ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন তা হচ্ছে ঃ ‘ইল্ম্, ‘আমল্ ও দূরদৃষ্টি। এ ক্ষেত্রে ‘ইল্ম্-এর অবস্থান সর্বাগ্রে, কারণ, যথাযথ ‘ইল্ম্-এর অধিকারী নন এমন ব্যক্তি ইখলাছ¡ ও “তাক্বওয়া’-র অধিকারী হলেও তাঁর ইখ্লাছ¡ তাঁকে দ্বীনী ও শর‘ঈ বিষয়াদিতে সঠিক ফয়সালা প্রদানের যোগ্যতার অধিকারী করবে না। অন্যদিকে যথাযথ ‘ইল্ম্ ব্যতিরেকে কারো পক্ষে প্রকৃত অর্থে “তাক্বওয়া’-র অধিকারী হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। কারণ, যথাযথ ‘ইল্ম্-এর অধিকারী নন এমন ব্যক্তি ফরযকে মুস্তাহাব, মুস্তাহাবকে ফরয, মোবাহ্কে হারাম ও হারামকে মোবাহ্ গণ্য করে বসতে পারেন এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে বসতে পারেন। যেহেতু “তাক্বওয়া’-র মানে বিশেষ ধরনের দাড়ি, বিশেষ কাটিং-এর পোশাক, নফল ‘ইবাদত ও তাসবীহ্-তাহ্লীল নয়, বরং “তাক্বওয়া’-র মানে আল্লাহ্ তা‘আলার আদেশ-নিষেধকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা এবং কোনো ক্ষেত্রে কমতি-বাড়তি বা বাড়াবাড়ি না করা যে জন্য যথাযথ ‘ইল্ম্ থাকা অপরিহার্য। আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ করেন ঃ
إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء
“নিঃসন্দেহে আল্লাহর বান্দাহ্দের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে।” (সূরাহ্ আল্-ফাতির ঃ ২৮)
আর ‘ইল্মের অধিকারী ব্যক্তির সাথে অন্যদের তুলনা হতে পারে না। আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ করেন ঃ
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَ
“(হে রাসূল!) আপনি বলুন ঃ যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?” (সূরাহ্ আয্-যুমারঃ ৯)
অবশ্য কেবল প্রকৃত অর্থে ও যথাযথ জ্ঞানের অধিকারী হলেই কারো পক্ষে আল্লাহ্কে ভয় করা সম্ভব এবং এ আয়াতে ‘জ্ঞানী’ (‘আলেম) বলতে এ ধরনের লোকদেরকেই বুঝানো হয়েছে, ‘আলেম হিসেবে পরিচিত যে কোনো লোককে নয়। অতএব, সত্যিকারের ‘আলেম হলে তিনি অবশ্যই যথাযথ ‘আমলের তথা তাক্বওয়ার অধিকারী হবেন এবং ওপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, তাক্বওয়ার অধিকারী ব্যক্তি দ্বীন ও শারী‘আহ্ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা‘আলার নির্ধারণের চেয়ে কমতি-বাড়তি করতে পারেন না তথা এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে পারেন না। সুতরাং তিনি হবেন চরম পন্থা (ইফ্রাত্) ও শিথিল পন্থা (তাফ্রীত্) থেকে মুক্ত তথা ভারসাম্যের (‘আদ্ল্-এর) অধিকারী মধ্যম পন্থার অনুসারী (উম্মাতে ওয়াসাত্ব)। যেহেতু আল্লাহ্ তা‘আলা ঈমানদারদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন ঃ لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ “তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অগ্রবর্তী হয়ো না।” (সূরাহ্ আল্-হুজুরাত্ ঃ ১) সেহেতু তিনি ইসলামের স্বার্থচিন্তা থেকেও আল্লাহ্ ও রাসূলের (সাঃ) নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করবেন না।
তৃতীয়তঃ দ্বীনী নেতৃত্বের জন্য এমন ব্যক্তিকে বেছে নেয়া অপরিহার্য যার মধ্যে উপরোক্ত দু’টি গুণ ছাড়াও দূরদৃষ্টি (بصيرت) রয়েছে যাতে তিনি পরিস্থিতি বিবেচনা করে উম্মাহ্কে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিতে পারেন। আমরা নবী-রাসূলগণের (আঃ) জীবনেও যাদের সকলেই ছিলেন গুনাহ্ ও ভুলের উর্ধে এর দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। তাঁরা পরিস্থিতি অনুযায়ী কর্মনীতি গ্রহণ করেন।
তার চেয়েও বড় কথা, এককভাবে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর জীবনে পরিস্থিতি বিবেচনায় যথোপযুক্ত বিভিন্ন কর্মনীতি অনুসরণের অনেকগুলো দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন ঃ তিনি নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ লাভের পর প্রথম তিন বছর অত্যন্ত গোপনে বেছে বেছে সুনির্দিষ্ট ও স্বল্পসংখ্যক লোকের কাছে তাঁর দাওয়াত পেশ করেন। এরপর তিনি মক্কায় আরো দশ বছর অহিংস ও প্রতিরোধবিহীন কর্মনীতি অনুসরণ করে প্রচারতৎপরতা চালান; এ সময়ের মধ্যে তিনি মুসলমানদের কতককে হিজরতে পাঠান এবং কিছুদিন অবরুদ্ধ জীবনও কাটান। এরপর তিনি হিজরত করেন, উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে মদীনায় হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন এবং সে হুকুমতে ইয়াহূদীদের নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ অবস্থানের সুযোগ দিয়ে ঘোষণাপত্র জারী করেন। মদীনার জীবনে তিনি যুদ্ধ করেন, সন্ধি করেন ও পত্রযোগাযোগ করেন তথা কূটনৈতিক তৎপরতা চালান। তিনি এমন সব শর্তাবলী সহকারে হুদায়বীয়্যাহর সন্ধি সম্পাদন করেন যা দৃশ্যতঃ তাঁর ও ইসলামের জন্য অপমানজনক ছিলো যে কারণে কতক ছাহাবী এতে আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু এ সন্ধি ইসলামের জন্য বিরাট কল্যাণ বয়ে এনেছিলো সন্ধি সম্পাদিত হবার পর পরই আল্লাহ্ তা‘আলা আয়াত নাযিল করে এ সন্ধিকে ‘সুস্পষ্ট বিজয়’ বলে আখ্যায়িত করে যে কল্যাণ সম্বন্ধে অগ্রিম সুসংবাদ প্রদান করেন।
বস্তুতঃ পাপ ও ভুল থেকে মুক্ত থাকার নিশ্চয়তা নেই এমন কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এতো বিচিত্র ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে যথাযথ কর্মনীতি গ্রহণ করা সম্ভব নয়।
মোদ্দা কথা, নবী-রাসূলের অবর্তমানে মুসলমানদের পরিচালনা, নেতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্বের জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে যদি কাউকে মনোনীত করে না-ও দেয়া হয় তথাপি ইখলাছের দাবী অনুযায়ী মু’মিনদের কর্তব্য হচ্ছে এ ধরনের গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তির ওপরে এ দায়িত্ব অর্পণ করা। অতএব, এ থেকে সুস্পষ্ট যে, হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ওফাতের পরে মুসলমানদের জন্য হযরত আলী (রাঃ)-এর ওপর নেতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করা অপরিহার্য ছিলো। কিন্তু তা হয় নি এবং না হওয়ার ফলে ইসলামী উম্মাহ্র মধ্যে যে বিভেদ-অনৈক্য ও বিভ্রান্তির ধারাবাহিকতার সূচনা হয় তা কারোই অজানা নয়।
এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত জরুরী বলে মনে করি।
আমাদের অনেকের মধ্যে মুসলমানদের ইতিহাস, বিশেষ করে ছাহাবীগণের ব্যাপারে এমন একটি প্রবণতা আছে যা বিচারবুদ্ধি (‘আক্বল্) ও কোরআন মজীদ সমর্থন করে না। তা হচ্ছে, ঢালাওভাবে ছাহাবীগণের প্রতি অন্ধ ভক্তি পোষণ করা যার ফলে তাঁদের অনেকের ভুলত্র“টি আমাদের মধ্যে অব্যাহত থেকে যাচ্ছে। মুসলমানদের অকাট্য ঐতিহাসিক বর্ণনা ও ছহীহ্ হিসেবে চিহ্নিত বহু হাদীছ থেকে যেখানে তাঁদের অনেকের বহু ভুল-ত্র“টির কথা জানা যায়, এমনকি জানা যায় যে, স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) তাঁদের কতককে বিভিন্ন ধরনের কঠিন অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছেন এবং তাঁর পরে তাঁরা পরস্পর যুদ্ধ করেছেন ও পরস্পরকে হত্যা করেছেন, তা সত্ত্বেও ঢালাওভাবে ছাহাবীদের সকলকে নক্ষত্রতুল্য, অনুসরণীয় ও সমালোচনার উর্ধে গণ্য করা হচ্ছে এবং সারা দুনিয়া যে বিষয়গুলো জানে তা থেকে স্বয়ং মুসলমানদের না-ওয়াক্বিফ্ রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। যারা তা করছেন তাঁরা ভেবে দেখতে প্রস্তুত নন যে, ছাহাবীদের সকলের নক্ষত্রতুল্য হওয়া সংক্রান্ত হাদীছটি হাদীছ-বর্ণনার সুদীর্ঘ পরম্পরার মধ্যে কোনো এক পর্যায়ে মিথ্যা রচিত হয়ে থাকতে পারে অথবা হয়তো হাদীছ সঠিক কিন্তু ‘ছাহাবী’র যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা ঠিক নয়, অর্থাৎ কেবল ঈমানের ‘ঘোষণা’ সহকারে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)কে দেখাই ‘ছাহাবী’ হওয়া প্রমাণ করে না, বরং শারীরিক ও আত্মিক উভয় দিক থেকে তাঁর সাহচর্যই (معيت جسمانی و روحانی) কারো ‘ছাহাবী’ হওয়া প্রমাণ করে।
এ অন্ধ ভক্তির কারণেই অনেককে ছাহাবীগণের শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে চার খলীফাহ্কে তাঁদের পর্যায়ক্রম অনুযায়ী সকলের উর্ধে স্থান দিতে দেখা যায়। এটা কতই না ভুল নীতি যে, যেহেতু তাঁরা চারজন পর্যায়ক্রমে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন সেহেতু তাঁদেরকে পর্যায়ক্রমে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেয়া হয়েছে! ঘটনাক্রমে যদি তাঁদের পরিবর্তে অন্য ছাহাবীদের মধ্য থেকে কয়েক জন ছাহাবী খলীফাহ্ হতেন তাহলে এরা তাঁদেরকেই পর্যায়ক্রমে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিতেন। উদাহরণস্বরূপ, ছয় সদস্যের নির্বাচনী কমিটির মধ্য থেকে যদি অন্য কেউ তৃতীয় খলীফাহ্ হতেন তাহলে তাঁরা তাঁকেই তৃতীয় শ্রেষ্ঠ ছাহাবীর মর্যাদা দিতেন। (!!)
অথচ গুণাবলীর বিচারে অনস্বীকার্য সত্য হলো এই যে, ছাহাবীগণের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। বিশেষ করে তিনি সাবালেগ হওয়ার তথা র্শিক্ ও গুনাহ্ প্রযোজ্য হওয়ার বয়সে উপনীত হওয়ার আগেই ইসলামের ছায়াতলে স্থানলাভ করেন এবং মুহূর্তের তরেও র্শিকী যিন্দেগী যাপন করেন নি। সন্দেহ নেই যে, ইসলাম গ্রহণ অতীতের র্শিক্ ও গুনাহ্কে মুছে দেয় এবং ব্যক্তি আর সে জন্য শাস্তিযোগ্য থাকে না। কিন্তু এ সত্ত্বেও এরূপ ব্যক্তি এবং যে ব্যক্তি জীবনে কখনো র্শিক্ বা অন্য কোনো গুনাহে লিপ্ত হন নি এ দুই ব্যক্তি কখনো এক হতে পারেন না, ঠিক যেভাবে একটি নতুন কাগজে ছবি আঁকা হলে এবং একই ছবি একটি ছবিযুক্ত কাগজের ছবি মুছে তার ওপরে আঁকা হলে দু’টি ছবি গুণের দিক থেকে অভিন্ন হতে পারে না।
এমনকি এ প্রশ্নটি বাদ দিলেও এবং তাক্বওয়া ও বাছীরাতের দৃষ্টিতে কে অগ্রগণ্য সে প্রশ্নও পাশে সরিয়ে রাখলে যেহেতু সর্বসম্মত মত অনুযায়ী ‘ইল্মের ক্ষেত্রে ছাহাবীগণের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ্ তা‘আলা কোরআন মজীদে আলেমের যে মর্যাদা বর্ণনা করেছেন তার ভিত্তিতে তিনি যে ছাহাবীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন তা অস্বীকার করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। অতঃপর, কেবল এর ভিত্তিতে ক্রমবিন্যাস করা হলে (এবং আহলে বাইতের অপর ব্যক্তিত্ববর্গের যারা ছাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁদের বিষয়টি বিবেচনায় না নিলেও) শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে হযরত আলী (রাঃ)-এর মর্যাদা সবার ওপরে, অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মর্যাদা; (তর্কের খাতিরে মেনে নিলে) অপর তিন খলীফাহর মর্যাদা বড় জোর তৃতীয় থেকে পঞ্চম হতে পারে।
অনুরূপভাবে, অর্থাৎ আমরা যদি ধরে নেই যে, আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর পরে কাউকে নেতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্বের জন্য মনোনীত করেন নি, তাহলেও সকল বিচারে যে হযরত আলী (রাঃ)কে এবং তাঁর পরে যথাক্রমে হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ)কে খেলাফতে অধিষ্ঠিত করা অপরিহার্য ছিলো সে ব্যাপারে দ্বিমতের কোনোই অবকাশ নেই। এমনকি যারা চার খলীফাহ্র খেলাফত্কেই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে গণ্য করেন তাঁরাও হযরত আলী (রাঃ)-এর পরে যথাক্রমে হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ)-এর খেলাফতের অধিকারকে স্বীকার করেন।
আদর্শিক ও বংশগত উত্তরাধিকারের অভিন্নতা প্রসঙ্গে
এমনও কেউ কেউ আছেন যারা আহলে বাইতের নেতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্বের অধিকারকে অস্বীকার করার লক্ষ্যে যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, ইসলামে বংশগত শ্রেষ্ঠত্বের তথা বংশগত নেতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্বের কোনো স্থান নেই। কেউ কেউ আরো এক ধাপ এগিয়ে এ ব্যাপারে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করে থাকেন এবং আহলে বাইতের নেতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্বের অধিকার প্রত্যাখ্যানের লক্ষ্যে এ মতকে কটাক্ষ করে রাজতন্ত্রের সাথে তুলনা করে বলেন, ইসলামে রাজতন্ত্রের স্থান নেই। আর এতে কিছু লোকের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। তাই এ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করা অপরিহার্য।
ইসলামে যে বংশগত শ্রেষ্ঠত্বের তথা বংশগত নেতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্বের এবং রাজতন্ত্রের স্থান নেই, এ ব্যাপারে বিতর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু আহলে বাইতের দ্বীনী নেতৃত্বের সাথে এর কোনোই সম্পর্ক নেই। কারণ, যাদেরকে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা করা হয়েছে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সাথে তাঁদের বংশগত ও আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে নয়, বরং তাঁদের গুণাবলীর কারণে। অতীতের নবী-রাসূলগণের (আঃ) ক্ষেত্রেও একই নীতি কার্যকর ছিলো।
অতীতের নবী-রাসূলগণ (আঃ) নবী-রাসূলগণের (আঃ) বংশধারায়ই আগমন করেন, কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কেবল নবী-রাসূলগণের (আঃ) বংশধর হওয়ার কারণেই কাউকে নবুওয়াত্ প্রদান করা হয় নি এবং নবী-রাসূলগণের (আঃ) বংশধরদের সকলকেই নবী-রাসূল মনোনীত করা হয় নি।
আল্লাহ্ তা‘আলা নবী-রাসূলগণের (আঃ) মনোনয়ন সম্বন্ধে এরশাদ করেন ঃ
إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
“অবশ্যই আল্লাহ্ জগতবাসীদের ওপরে আদম, নূহ্, আালে ইবরাহীম ও আালে ‘ইমরান-কে নির্বাচিত করেছেন; তাদের কতক অপর কতকের বংশধর।” (সূরাহ্ আালে ইমরান ঃ ৩৩-৩৪)
ইমামত বা দ্বীনী নেতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্বের বিষয়টিও অনুরূপ। আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে ইমাম নিয়োগের কথা জানানো হলে ইবরাহীম (আঃ) এ অঙ্গীকার তাঁর বংশধরদের বেলাও প্রযোজ্য কিনা জানতে চান, তখন আল্লাহ্ তা‘আলা যে জবাব দেন যা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে এটি প্রমাণিত হয়।
আল্লাহ্ তা‘আলার ফয়সালার যথার্থতা সম্বন্ধে কারো মনে কোনোরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্বের উদ্রেক হলে তা সুস্পষ্টই ঈমানের পরিপন্থী। তবে এর যথার্থতার ওপর পরিপূর্ণ আস্থা সহকারে বাস্তবতার আলোকে এর কারণ জানার চেষ্টা করা দূষণীয় নয়, বরং তা ঈমান মজবূত হবার কারণ হতে পারে।
এ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, নবুওয়াত-রিসালত ও দ্বীনী ইমামতের দায়িত্ব পালনের জন্য পাপ ও ভুলের উর্ধে থাকার নিশ্চয়তা থাকা অপরিহার্য। আর এ নিশ্চয়তার জন্য রক্তধারার পরিপূর্ণ পবিত্রতাও অপরিহার্য।
অবশ্য পবিত্র রক্তধারার অধস্তন বংশধরদের মধ্যে পাপ ও অপবিত্রতা প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু পাপ ও অপবিত্রতার অধিকারী কোনো ব্যক্তির পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে এ থেকে মুক্ত থাকা অসম্ভব না হলেও তার নিশ্চয়তা থাকে না এবং বাস্তবে এ ধরনের কোনো ব্যক্তির মনস্তাত্বিক গঠন সর্বস্তরে পবিত্রতার অধিকারী রক্তধারায় আগত নিষ্পাপ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে না। তাই বিচারবুদ্ধির দাবী হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা‘আলার সৃষ্টিলক্ষ্যের চূড়ান্ত বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা বিধানের স্বার্থে তিনি সৃষ্টিপরিকল্পনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ই এর মৌলিক কাঠামো তথা যাদেরকে নবী-রাসূল ও নিষ্পাপ দ্বীনী ইমাম হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করবেন তাঁদেরকে সুনির্দিষ্ট করে রাখবেন, আর সে ক্ষেত্রে তাঁদেরকে নিষ্পাপ ও পবিত্র রক্তধারার মধ্যেই নির্ধারণ করে রাখবেন এটাই স্বাভাবিক; যাদের পাপমুক্ততা ও ভুলের উর্ধে হওয়ার বিষয়টি অনিশ্চিত তাদের মধ্য থেকে নয়।
অধিকতর বাস্তব সত্য এই যে, আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর নবী-রাসূল ও নিষ্পাপ দ্বীনী ইমাম সহ যে সব খাছ¡ বান্দাহ্কে সৃষ্টি করার বিষয়টি তাঁর সৃষ্টিপরিকল্পনার অংশ হিসেবে সৃষ্টির শুরুতে নির্ধারণ করে রাখেন তাঁরা ব্যতীত অন্য সকলের দুনিয়ার বুকে আগমনের বিষয়টি ছিলো এজমালী এবং আল্লাহ্ তা‘আলার নির্ধারিত ‘কারণ ও ফলশ্র“তি’ Cause and Effect Ñ علت و معلول) বিধির ওপর নির্ভরশীল, সুনির্দিষ্ট নয়।
এর মানে হচ্ছে, আল্লাহ্ তা‘আলার সৃষ্টিপরিকল্পনা অনুযায়ী হযরত আদম (আঃ)-এর বংশে হাজার হাজার কোটি ‘মানুষ’ আগমনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকলেও আপনার-আমার মতো লোকদের আগমন নির্ধারিত ছিলো না, বরং ‘কারণ ও ফলশ্র“তি’ বিধির আওতায় আপনার-আমার আগমন অপরিহার্য হয়ে ওঠার কারণেই আপনার-আমার মতো লোকদের আগমন ঘটে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলার সৃষ্টিপরিকল্পনায় নবী-রাসূলগণ, নিষ্পাপ দ্বীনী ইমামগণ ও আরো কতক খাছ¡ বান্দাহর [যেমন ঃ হযরত র্মাইয়াম (আঃ) ও হযরত ফাতেমাহ্ (রাঃ)] অন্তর্ভুক্তি ছিলো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি Proper Noun) হিসেবে [অনেক লোকের ভ্রান্ত ধারণার বরখেলাফে নবী-রাসূলগণ, নিষ্পাপ ইমামগণ ও অপর কতক খাছ¡ বান্দাহর বিষয়টি যে আল্লাহ্ তা‘আলার সৃষ্টিপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ছিলো শুধু তা-ই নয়, এমনকি তাঁদের নাম-ও পূর্ব থেকে নির্ধারিত ছিলো। কোরআন মজীদে হযরত ইসমা‘ঈল, হযরত ইস্হাক্ব, হযরত ইয়া‘কূব, হযরত মূসা, হযরত ‘ঈসা ও হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর নবুওয়াত্ সম্পর্কে তাঁদের জন্মের আগেই নামোল্লেখ সহ সুসংবাদ দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনি হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর নামও পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিলো। কোরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ‘ঈসা (আঃ) তাঁর ‘আহ্মাদ্’ নাম উল্লেখ করে তাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেন (সূরাহ্ আছ-ছাফ্ ঃ ৬)। এছাড়া ইসলামের সকল মাযহাব ও ফির্কাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হাদীছ অনুযায়ী, হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ্ তা‘আলার ‘আরশে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) ও তাঁর আহলে বাইতের চার পবিত্র ব্যক্তিত্বের নূরানী রূপ ও ‘নাম’ দেখতে পান এবং তাঁদেরকে উসিলাহ্ করে আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এ বিষয়টি ইয়াহূদীদের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ ‘ইদরীস (আঃ)-এর কিতাব’-এও উল্লেখ করা হয়েছে।]এবং অন্য সকলের অন্তর্ভুক্তি ছিলো কেবল ‘মানুষ’ Common Noun) হিসেবে।[ রক্তধারার পবিত্রতা ঃ একটি বিভ্রান্তির নিরসন
ইতিপুর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে (সূরাহ্ আালে ‘ইম্রান্ ঃ ৩৩-৩৪) নবী-রাসূলগণ (আঃ) হচ্ছেন ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ (কতক অপর কতকের বংশধর)। এ আয়াতাংশ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, কোনো নবী-রাসূলের (আঃ) (তেমনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত যে কোনো নিষ্পাপ ইমামের) পূর্বতন রক্তধারায় কখনোই র্শিক ও গুনাহের সংমিশ্রণ ঘটে নি। যদিও ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ বলতে কেবল একে অপরের অব্যবহিত বংশধরই বুঝায় না, বরং মধ্যবর্তী স্তরে এক বা একাধিক অ-নবী সহ পরবর্তী বংশধরও বুঝায়, কিন্তু এ মধ্যবর্তী স্তরগুলোতে যদি র্শিক্ ও গুনাহের সংমিশ্রণ ঘটে তাহলে পরবর্তী স্তরের নবীকে (এবং সেই সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত নবীর গুণাবলী সম্পন্ন নিষ্পাপ ইমামকে) পূর্ববর্তী নবীর বংশধর বুঝাতে ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ -এর উল্লেখ অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, সে ক্ষেত্রে কথাটি দাঁড়ায় আল্লাহর নবী হযরত আদম (আঃ)-এর বংশধর হিসেবে নমরূদ ও র্ফিআউন্ সহ সমস্ত মানুষকে নবীর বংশধর বলে উল্লেখ করার অনুরূপ যার উল্লেখ অর্থহীন বৈ নয়। আর আল্লাহ্ তা‘আলা যে কোনো ধরনের অর্থহীন কথা ও কাজ থেকে প্রমুক্ত। অতএব, সন্দেহ নেই যে, এটি আল্লাহ্ তা‘আলার একটি নীতি যে, তিনি যে কোনো নবী-রাসূলকেই (এবং তাঁর পক্ষ থেকে মনোনীত নবীর গুণাবলী সম্পন্ন নিষ্পাপ ইমামকে) এমন রক্তধারায় পাঠিয়েছেন যাতে কখনোই র্শিক্ বা গুনাহের সংমিশ্রণ ঘটে নি।
কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতৃপরিচয় সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার কারণে অনেকেই এটিকে আল্লাহ্ তা‘আলার একটি নীতি হিসেবে গণ্য করতে প্রস্তুত নন।
যদিও এ বিষয়টি নবী-রাসূলগণের (আঃ) পাপমুক্ততা (عصمة الانبياء) সম্পর্কিত আলোচনায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা সর্বোত্তম এবং অত্র গ্রন্থকারের রচনাধীন গ্রন্থ ‘নবী-রাসূলগণের (আঃ) পাপমুক্ততা’য় এ সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, তবে আলোচ্য পুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে প্রাসঙ্গিক বিধায় এখানেও আমরা সংক্ষেপে বিষয়টির ওপর আলোকপাত করছি।
কোরআন মজীদের সূরাহ্ আল্-আন্‘আামের ৭৪ নং আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক আর্য ও তার সম্প্রদায়ের মূর্তিপূজার সমালোচনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ابيه آزر (তার “আব্” আর্যা) উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ থেকেই আর্য-কে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ‘জন্মদাতা পিতা’ বলে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে এটা নিশ্চিতরূপে ধরে নেয়া সম্ভব নয় যে, আর্য তাঁর জন্মদাতা পিতা ছিলো। কারণ, আরবী ভাষায় “আব্” (বাক্যমধ্যে ভূমিকাভেদে ابو/ ابا/ ابی) শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক যা দ্বারা জন্মদাতা পিতা ছাড়াও দাদা, চাচা, পালক পিতা ও বিপিতাকে এবং দাদার পূর্ববর্তী যে কোনো পূর্বপুরুষকেও বুঝানো হয়। কিন্তু শুধু জন্মদাতা পিতা বুঝানো উদ্দেশ্য হলে “ওয়ালেদ” (والد) বলা হয়।
এমতাবস্থায় কয়েকটি কারণে উক্ত আয়াতে আযরকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্মদাতা পিতা বুঝানো হয়েছে বলে মনে করা যায় না। তা হচ্ছে ঃ
১) আল্লাহ্ তা‘আলা জানতেন যে, এ বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে, এমতাবস্থায় জন্মদাতা পিতা বুঝানো উদ্দেশ্য হলে ابيه না বলে والده বললে বিভ্রান্তির কোনোই অবকাশ থাকতো না। অথবা শুধু ابيه বলা হতো, আযরের নামোল্লেখ করার প্রয়োজন ছিলো না। কারণ, যেহেতু শব্দটির প্রথম অর্থ ‘জন্মদাতা পিতা’ সেহেতু এর সাথে অন্য অর্থজ্ঞাপক নিদর্শন না থাকলে এ থেকে ‘জন্মদাতা পিতা’ ছাড়া অন্য অর্থ গ্রহণের কোনোই কারণ থাকতো না। এমতাবস্থায় নিদর্শন জুড়ে দেয়া অর্থাৎ আযরের নামোল্লেখ থেকে সুস্পষ্ট যে, এখানে শব্দটিকে এর প্রথম অর্থে ব্যবহার করা হয় নি, বরং বুঝানো হয়েছে যে, এখানে ابيه বলতে তাঁর জন্মদাতাকে বুঝানো হয় নি, বরং আর্যকে (যে সম্ভবতঃ তাঁর পালক পিতা ছিলো) বুঝানো হয়েছে।
২) বিদ্যমান তাওরাতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্মদাতা পিতার নাম ‘তেরহ্’ বা ‘তারেহ্’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় কোরআন মজীদে তাঁর জন্মদাতা পিতার নাম “আর্য” বলে উল্লেখ করা হলে তৎকালীন ইয়াহূদী ও খৃস্টান পণ্ডিতরা এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতো ও এর ভিত্তিতে দাবী করতো যে, কোরআন আল্লাহর কালাম নয় বলেই এতে ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে এবং এ নিয়ে তারা ব্যাপক প্রচার চালাতো। কিন্তু এ ধরনের প্রতিবাদ ও দাবীর কথা জানা যায় না। এ থেকে বুঝা যায় যে, তৎকালীন ইয়াহূদী ও খৃস্টান পণ্ডিতরা ابيه থেকে ‘জন্মদাতা পিতা’ অর্থ গ্রহণ করে নি।
৩) হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর নম্রহৃদয় বৈশিষ্ট্যের কারণে আযরের জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে মাগফেরাত কামনা করতেন, কিন্তু তাঁর কাছে যখন অকাট্যভাবে সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, সে আল্লাহর শত্র“ তখন তিনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন (এবং তার জন্য মাগফেরাত কামনা বন্ধ করে দিলেন)। (সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্ ঃ ১১৪)।
এটা কখনকার ঘটনা কোরআন মজীদে তা উল্লেখ করা হয় নি (উল্লেখের প্রয়োজনও ছিলো না), তবে এটা নিঃসন্দেহে ধরে নেয়া যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) অগ্নিকুণ্ড থেকে নিরাপদে বেরিয়ে এসে ফিলিস্তিনে হিজরতের আগেই তাঁর কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আযরের ঈমান আনার আর কোনোই সম্ভাবনা নেই। এ কারণে তিনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং তার জন্য মাগফেরাত কামনা বন্ধ করে দেন (সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্ ঃ ১১৪)। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, হিজরতের বহু বছর পরে তরুণ হযরত ইসমা‘ঈল (আঃ)কে মক্কায় আল্লাহর ঘরে পাশে রেখে আসার (সূরাহ্ ইবরাহীম ঃ ৩৭) সময় যার আগেই হযরত ইস্হাাক্ব (আঃ)-এর জন্ম হয়েছে ও তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন (সূরাহ্ ইবরাহীম ঃ ৩৯) (যখন তাঁর বয়স একশ’ বছর পেরিয়ে গেছে), তখন তিনি তাঁর পিতা-মাতার (والدي) মাগফেরাতের জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে দো‘আ করেন (সূরাহ্ ইবরাহীম ঃ ৪১)। এ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আর্য তাঁর জন্মদাতা পিতা ছিলো না।
এ উপসংহার থেকে আরো একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, যেহেতু হযরত আলী (রাঃ)-র আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার, উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হওয়ার, দ্বীনী নেতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্বের জন্য উপযুক্ততম ব্যক্তি হওয়ার এবং নবী না হয়েও পাপমুক্ততা সহ নবী-রাসূলগণের (আঃ) গুণাবলী সম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত সেহেতু তাঁর পিতৃপুরুষদের রক্তধারায় কখনো র্শিক্ ও গুনাহের সংমিশ্রণ ঘটে নি। অতএব, তাঁর পিতা হযরত আবূ ত্বাালিবের মুশরিক হওয়ার ও ইসলাম গ্রহণ না করার দাবী চরম রাজৗনতিক মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। বরং হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর পিতা আবদুল্লাহ্ ও দাদা আবদুল মুত্তালিবের ন্যায় তাঁর চাচা ও হযরত আলী (রাঃ)-এর পিতা হযরত আবূ ত্বাালিব্-ও র্শিক্ ও গুনাহ্ থেকে মুক্ত তাওহীদবাদী ছিলেন, আর নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক ইসলাম প্রচারের সূচনাতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ কারণেই তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নবী করীম (সাঃ)কে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করেছিলেন।
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, হযরত আবূ ত্বালিব্ কর্তৃক নবী করীম (সাঃ)কে আশ্রয়, পৃষ্ঠপোষকতা ও সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের বিষয়টি ইসলামের ইতিহাসের একটি বিতর্কাতীত বিষয় যে ব্যাপারে ইসলামের সকল মাযহাব ও ফির্ক্বাহর মধ্যে ইজ্মা ‘ রয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কি সম্ভব যে, নবীকূলশিরোমণি হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ লাভের পরেও বছরের পর বছর ধরে একজন মুশরিকের আশ্রয়ে থাকবেন এবং তার কাছ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করবেন? এরূপ হলে তা কি ইসলামের জন্য একটি লজ্জাজনক ও অপমানজনক বিষয় হতো না? এমনকি স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলার জন্যও কি তাঁর শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূলকে এরূপ লজ্জাজনক ও অপমানজনক অবস্থায় রেখে দেয়া সম্ভব? অতএব, হযরত আবূ ত্বাালিব্ মুশরিক ছিলেন বলে যে দাবী করা হয়েছে তা যে স্রেফ রাজনৈতিক মিথ্যাচার ছিলো এ ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই। [এ ধরনের রাজনৈতিক মিথ্যাচারের দৃষ্টান্ত ইসলামের ইতিহাসে আরো অনেক আছে। হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ)কে ক্ষমতালোভী বলে প্রচার করা হয়েছিলো, আর হযরত আলী (রাঃ) যখন কূফাহ্র মসজিদে ঘাতকের তলোয়ারের আঘাতে আহত হয়ে পরে শাহাদাত বরণ করেন সে খবর দামেশ্ক্বে পৌঁছলে অনেক লোক বিস্মিত হয়ে বলেছিলো ঃ আলী মসজিদে গিয়েছিলো কী জন্য?! সে কি নামাযও পড়তো নাকি?!]
পাপমুক্ততা ও এখ্তিয়ার-এর সমন্বয় কীভাবে
অনেকের ধারণা যে, নবী-রাসূলগণ এবং আল্লাহ্ তা‘আলার মনোনীত ইমামগণ ও অন্যান্য খাছ¡ বান্দাহ্র পাপমুক্ততা (عصمة)-এর মানে এই যে, তাঁদের মধ্যে গুনাহ্ করার ক্ষমতাই দেয়া হয় নি। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। কারণ, তাঁদের মধ্যে গুনাহ্ করার ক্ষমতা না থাকলে তাঁরা ফেরেশতার পর্যায়ে গণ্য হতেন এবং সে ক্ষেত্রে তাঁরা মানুষের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হতেন না। বস্তুতঃ তাঁদের মধ্যে গুনাহ্ করার ক্ষমতাই ছিলো না বলে ধরে নেয়ার কারণে অনেক লোক নিজেদের গুনাহ্র সপক্ষে এটিকে বাহানা হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো তাঁদের মধ্য থেকে গুনাহ্ করার ক্ষমতা বিলুপ্ত করা হয় নি, সুতরাং তাঁদের অবস্থাকে বাহানা হিসেবে গণ্য করে কারো পক্ষে গুনাহ্ করে পার পেয়ে যাবার কোনোই সুযোগ নেই।
এ বিষয়টিও মূলতঃ ‘নবী-রাসূলগণের (আঃ) পাপমুক্ততা’ সংক্রান্ত আলোচনায় আলোচিতব্য বিষয় এবং উপরোক্ত শিরোনামে অত্র গ্রন্থকারের রচনাধীন গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। তবে অত্র পুস্তকের আলোচ্য বিষয়ের সাথে এর সম্পর্ক থাকায় এখানেও বিষয়টির ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।
বস্তুতঃ নিষ্পাপ ব্যক্তিগণের মধ্যে গুনাহ্ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা স্বেচ্ছায় গুনাহ্ থেকে বিরত থাকেন। এটা সম্ভব হয় তাঁদের রক্তধারার পবিত্রতা, ঈমানের গভীরতা ও দৃঢ়তা এবং পূত-পবিত্র জীবন যাপনে অভ্যস্ততার কারণে। এর ফলে তাঁদের মধ্যে পাপ না করার বিষয়টি তাঁদের গোটা সত্তার (শরীর ও নাফ্স্ উভয়ের) অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়ে যায়। ফলে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কিছুতেই তাঁরা গুনাহে লিপ্ত হন না এবং তাঁদের সত্তা গুনাহকে গ্রহণ করে না।[ গ্রন্থকারের বাল্যকালে শোনা একটি ঘটনার দৃষ্টান্ত দেয়া হলে বিষয়টি বুঝতে পারা সহজতর হবে বলে মনে করি। ঘটনাটি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সংক্ষেপে তা হলো ঃ দু’জন (বা তিনজন) মুসলমান (!) চোর একজন হিন্দুর ঘরে সিঁদেল চুরি করে বিভিন্ন মালামাল বাইরে এনে এরপর রান্নাঘরে ঢোকে হাঁড়িপাতিল নেয়ার জন্য। সেখানে একটি পাত্রে তৈরী রুটি ও একটি পাতিলে রান্না করা মাংস পেয়ে তাকে পাঠার মাংস মনে করে রুটি-মাংস খেতে শুরু করে। এক পর্যায়ে মাংসের ভিতর কাছিমের পা আবিষ্কৃত হলে তাদের বমি শুরু হয়ে যায় এবং পেট পুরোপুরি খালি হয়ে যাবার পরেও বমির ভাব বন্ধ হয় না, বরং নাড়িভুঁড়িও বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়।
এমনটা কেন হলো?
চুরি করে অন্যের সম্পদ ভোগ করা এবং চুরি করে অন্যের খাবার খাওয়া হারাম জানা সত্ত্বেও তাদের জ্ঞান ও ঈমান তাদেরকে চুরি থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে নি, কারণ, তাদের সে ঈমান ছিলো অগভীর। কিন্তু কাছিম হারাম হবার ব্যাপারে তাদের জ্ঞান ও ঈমান তাদের সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। এ কারণে তাদের পাকস্থলী কাছিমকে কাছিম বলে জানার পরে আর তার মাংসকে গ্রহণ করতে রাযী হয় নি, যদিও পাঠা বলে জানা অবস্থায় তা গ্রহণ করতে আপত্তি করে নি। অথচ ইসলামী শারী‘আতে যা কিছু খাওয়া হারাম করা হয়েছে জীবন বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পরিমাণে তা খাওয়ার অনুমতি আছে এবং তাতে গুনাহ্ হবে না; জীবন বাঁচানোর জন্যও চুরি করে গরুর গোশত খাওয়ার তুলনায় ইঁদুর-বিড়ালের মাংস খাওয়া অপেক্ষাকৃত উত্তম, কারণ, প্রথম ক্ষেত্রে কম হলেও গুনাহ্ হবে, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গুনাহ্ হবে না।
উপরোক্ত ঘটনায় কাছিম হারাম হওয়ার জ্ঞান ও ঈমান যেভাবে চোরদের সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো, একইভাবে আল্লাহ্ তা‘আলার যে কোনো নাফরমানী তথা যে কোনো গুনাহ্র কাজ সংক্রান্ত জ্ঞান ও ঈমান মা‘ছূম ব্যক্তিদের সত্তার অংশে পরিণত হয়ে যায়।]কিন্তু যেহেতু তাঁদের গুনাহ্ করার ক্ষমতা হরণ করা হয় নি সেহেতু এ সম্ভাবনা শূন্যের কাছাকাছি হলেও একেবারে শূন্য নয়। এ কারণেই আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি যদি আল্লাহর নামে কোনো কথা বানিয়ে বলতেন তাহলে তাঁকে কঠিনভাবে পাকড়াও করা হতো (সূরাহ্ আল-হাক্বক্বাহ্ ঃ ৪৪-৪৬)। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর থেকে আল্লাহর নামে কোনো কথা বানিয়ে বলার তথা যে কোনো ধরনের গুনাহে লিপ্ত হবার ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হয় নি। (অবশ্য ইন্তেকালের পরে রাসূলুল্লাহ্ সহ যে কোনো মা‘ছূম ব্যক্তিরই মা‘ছূম্ থাকার বিষয়টি সম্পর্কে আর কোনোরূপ অনিশ্চয়তা থাকে নি।)
সুতরাং কারো জন্য মা‘ছূমগণের নিষ্পাপ অবস্থাকে নিজের জন্য গুনাহ্র অনুকূলে বাহানা তৈরীর সুযোগ নেই। অন্যদিকে মা‘ছূম না হওয়ার মানেও এ নয় যে, কারো পক্ষেই সারা জীবন পাপমুক্ত থাকা সম্ভব নয়, বরং সারা জীবন ছোট-বড় যে কোনো ধরনের গুনাহ্ থেকে মুক্ত থাকা অন্যদের জন্য খুবই দুরূহ তথা ‘প্রায় অসম্ভব’ হলেও ‘পুরোপুরি অসম্ভব’ নয়।
সতর্কতার নীতি যা দাবী করে
কেউ যদি মনে করে যে, হযরত আলী (রাঃ)কে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর অব্যবহিত পরবর্তী নেতৃত্বের জন্য মনোনীত করার বিষয়টি আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে ছিলো না, বরং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তা নিজের পক্ষ থেকে করেছিলেন তাহলেও তা মেনে নেয়া উম্মাহ্র জন্য অপরিহার্য ছিলো। কারণ, সে ক্ষেত্রে নবী যে তাঁর অনুসারীদের ওপর তাঁদের নিজেদের চেয়েও অধিকতর অধিকার রাখেন (সূরাহ্ আল্-আহযাবঃ ৬) সে কারণে তাঁর সিদ্ধান্তের কাছে আত্মসমর্পণ করা অপরিহার্য ছিলো। কারণ, তিনি (‘ভাত খাবেন, নাকি রুটি খাবেন’ এ জাতীয় নেহায়েতই পার্থিব মোবাহ্ বিষয়াদি ব্যতীত) স্বীয় দায়িত্ব পালনের সাথে সম্পৃক্ত যে কোনো বিষয়ে আল্লাহ্ তা‘আলার প্রত্যক্ষ ওয়াহী (وحی متلو) বা পরোক্ষ ওয়াহী (وحی غير متلو)-এর ভিত্তিতে ছাড়া কখনো কিছু বলতেন না বা করতেন না। আর বলা বাহুল্য যে, নেতা বা উত্তরাধিকারী মনোনয়ন একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ।
আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ করেন ঃ
وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى
“তিনি স্বীয় প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না; তা (তিনি যা বলেন) তো ওয়াহী ছাড়া আর কিছু নয় যা তাঁকে পরমশক্তিধর শিক্ষা দান করেন।” (সূরাহ্ আন্-নাজ্ম্ ঃ ৩-৫)
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা মু’মিনদেরকে আরো নির্দেশ দিয়েছেন ঃ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا
“আর রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো এবং তিনি যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো।” (সূরাহ্ আল্-হাশর- ৭)
আর, খোদা না করুন, কেউ যদি মনে করে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারণ ছাড়াই বা (এরূপ নির্ধারণ না থাকার ক্ষেত্রে) সর্বোচ্চ যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কেবল স্বীয় জামাতা হওয়ার কারণেই হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে উম্মাহর জন্য পরবর্তী নেতা ও শাসক মনোনীত করে গেছেন তাহলে রিসালাত সম্পর্কে এরূপ ভ্রান্ত ‘আক্বীদাহ্ পোষণের কারণে তার ঈমানই বিনষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য। কারণ, পক্ষপাতিত্ব অত্যন্ত খারাপ ধরনের একটি বৈশিষ্ট্য হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) সহ সকল নবী-রাসূল (আঃ)ই যা থেকে পুরোপুরি মুক্ত ছিলেন।
অন্যদিকে কারো কাছে যদি ইখ্লাছ¡ সত্ত্বেও এরূপ মনে হয় যে, হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) গাদীরে খুমের ভাষণে হযরত আলী (রাঃ)কে যে উম্মাহর জন্য مولی বলে ঘোষণা করেছেন তাতে তিনি এ শব্দ দ্বারা ‘বন্ধু’ বুঝাতে চেয়েছেন, সে ক্ষেত্রেও যেহেতু এ শব্দের অন্যতম অর্থ ‘শাসক’ এবং স্বয়ং হযরত আলী (রাঃ) সহ কতক ছাহাবী এ থেকে এই শেষোক্ত অর্থই গ্রহণ করেছিলেন এবং এর ভিত্তিতে খেলাফতকে তাঁর হক বলে গণ্য করতেন সেহেতু ইসলামের সকল মাযহাব ও ফির্ক্বাহর কাছে গৃহীত ‘সতর্কতার নীতি’র দাবী অনুযায়ী তাঁকেই খেলাফত প্রদান করা কর্তব্য ছিলো। কারণ, যেহেতু, তাঁদের কাছে এ ব্যাপারে কোনো অকাট্য দলীল ছিলো না যে, হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর দ্বারা ‘বন্ধু’ বুঝিয়েছেন সেহেতু এতে ‘বন্ধু’ বুঝানো হলেও হযরত আলী (রাঃ)কে খলীফাহ্ করা হলে কোনো সমস্যা ছিলো না, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যদি এর দ্বারা ‘শাসক’ বুঝিয়ে থাকেন সে ক্ষেত্রে তাঁকে শাসকের দায়িত্ব প্রদান না করায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সিদ্ধান্ত কার্যকর করা থেকে বিরত থাকা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা‘আলার সুস্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে।
এছাড়া আহলে বাইতের পাপমুক্ততার অকাট্যতার কারণে বিচারবুদ্ধির অকাট্য রায় অনুযায়ী ইসলামের পরবর্তী নেতৃত্ব-কর্তৃত্বও আহলে বাইতের ধারাবাহিকতায় থাকা অপরিহার্য ছিলো। এমনকি নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব তাঁদেরকে অর্পণের বিষয়টি কারো কাছে যদি ফরয বলে পরিগণিত না-ও হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রেও সতর্কতার নীতির দাবী অনুযায়ী তা তাঁদেরকে অর্পণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা জরুরী ছিলো।
ইতিপূর্বে আমরা ইসলামের চারটি অকাট্য দ্বীনী জ্ঞানসূত্রের কথা উল্লেখ করেছি এবং খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছ সমূহ গ্রহণকে এ চার জ্ঞানসূত্রের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়ার শর্তসাপেক্ষ বলে উল্লেখ করেছি। এর মানে হচ্ছে, খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছ চোখ বুঁজে গ্রহণ করা যাবে না, তেমনি তা চোখ বুঁজে বর্জন করাও যাবে না; কেবল চারটি অকাট্য সূত্রের কোনোটির সাথে সাংঘর্ষিক হলেই তা বর্জন করা যাবে।
আমরা যেমন দেখেছি আহলে বাইতের (চার ব্যক্তিত্বের) পবিত্রতা ও পাপমুক্ততা এবং নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের অধিকার অন্ততঃ অগ্রাধিকার কোরআন মজীদ, মুতাওয়াতির হাদীছ ও (সতর্কতার নীতি সহ) ‘আক্বলের অকাট্য রায়ের দ্বারা প্রমাণিত। অনুরূপভাবে যেহেতু হযরত আলী (রাঃ)-এর ‘মাওলা’ হবার বিষয়টিও মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত এবং প্রাপ্ত ‘আক্বলী (বিচারবুদ্ধিজাত) ও নাক্বলী (বর্ণিত) সকল নিদর্শন থেকে এখানে এ পরিভাষাটির ‘নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্ব’ তাৎপর্য প্রমাণিত হয়, সেহেতু অন্ততঃ সতর্কতার নীতির দাবী অনুযায়ী এ তাৎপর্যের ভিত্তিতে আমল করা অপরিহার্য ছিলো।
এর সাথে যোগ করতে হয় যে, আরো বিভিন্ন হাদীছে, বিশেষ করে আহলে সুন্নাতের ধারাবাহিকতার অনেক হাদীছে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ওফাতের পরে হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) ও হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ) এবং হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ)-এর অধস্তন পুরুষ নয়জন পবিত্র ব্যক্তিত্বের নামোল্লেখ সহ পর্যায়ক্রমিক ইমামতের কথা বর্ণিত হয়েছে।
অনেক হাদীছ বিশেষজ্ঞের মতে এ সব হাদীছের মূল বক্তব্য মুতাওয়াতির পর্যায়ের। অবশ্য এর তাওয়াতুরের বিষয়টি গাদীরে খুমে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) কর্তৃক হযরত আলী (রাঃ)কে উম্মাহ্র জন্য ‘মাওলা’ ঘোষণার তাওয়াতুরের ন্যায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের নয়। এমতাবস্থায় অপর এগারো জন ব্যক্তিত্বের ইমামত সংক্রান্ত হাদীছ মুতাওয়াতির কিনা এ ব্যাপারে কারো পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলার অবকাশের কথা মাথায় রেখে এ সব হাদীছকে যুক্তির খাতিরে খবরে ওয়াহেদ্ বলে গণ্য করলেও একই বিষয়বস্তুতে এর সাথে সাংঘর্ষিক অনুরূপ পর্যায়ের হাদীছ না থাকায় এর ভিত্তিতে আমল করা অপরিহার্য। অর্থাৎ যেহেতু হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) থেকে অন্য কোনো লোকদের সম্পর্কে তাঁর পরে পর্যায়ক্রমিক ইমামতের কথা বর্ণিত হয় নি সেহেতু সতর্কতার নীতি অনুযায়ী তাঁদের ইমামতের বিষয়টি মেনে নেয়া অপরিহার্য।
আহলে সুন্নাতের ধারাবাহিকতার শীর্ষস্থানীয় অনেক দ্বীনী ব্যক্তিত্বই আহলে বাইতের ধারাবাহিকতার উক্ত বারো জন পবিত্র ব্যক্তিত্বের ইমামতকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে না নিলেও তাঁদের অনেকের উক্তি ও আচরণে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁরা উক্ত ব্যক্তিত্ববর্গকে উম্মাহর মধ্যে বিশিষ্ট দ্বীনী মর্যাদার অধিকারী বলে গণ্য করতেন। তাঁরা কখনোই উক্ত বারো জন ব্যক্তিত্বের সমালোচনা করতেন না এবং তাঁদের নিষ্পাপত্ব (عصمة)কে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার না করলেও কখনোই বলেন নি যে, তাঁরা মা‘ছূম ছিলেন না বা আর দশজন দ্বীনী বুযুর্গ ব্যক্তিত্বের অনুরূপ ছিলেন। এর ফলে সামগ্রিকভাবে আহলে সুন্নাতের অনুসারীদের কাছে তাঁরা অনুরূপ মর্যাদা লাভ করেছেন।
বিশেষ করে আমরা হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ) ও হযরত ইমাম মালেক (রহ্ঃ)কে যাদের নামে পরবর্তীকালে হানাফী মাযহাব ও মালেকী মাযহাবের নামকরণ করা হয়েছে আহলে বাইতের ধারাবাহিকতার হযরত ইমাম বাক্বের (রহ্ঃ) ও হযরত ইমাম জা‘র্ফা ছাদেক্ব (রহ্ঃ)-এর নিকট দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ করতে ও তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করতে দেখি। বিশেষ করে হযরত ইমাম জা‘র্ফা ছাদেক্ব (রহ্ঃ) সম্পর্কে হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ)-এর একটি উক্তি খুবই বিখ্যাত, তা হচ্ছে, তিনি বলেন ঃ “আমি জা‘র্ফা ইবনে মুহাম্মাদের চেয়ে বড় কোনো আলেমের সাক্ষাৎ পাই নি।”
হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ) ও হযরত ইমাম মালেক (রহ্ঃ) যে আহলে বাইত্-কে কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন তা তাঁদের আরো কোনো কোনো আচরণ থেকে প্রকাশ পায়। তা হচ্ছে, এমনকি আহলে বাইতের ধারাবাহিকতার যে সব বুযুর্গ ব্যক্তিত্বের জন্য উক্ত বারো জন ব্যক্তিত্বের ন্যায় আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে মনোনীত ইমাম হওয়া সংক্রান্ত হাদীছের বর্ণনা বিদ্যমান নেই কেবল আহলে বাইতের ধারাবাহিকতার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে অন্যদের তুলনায় তাঁদেরকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করতেন।
উদাহরণস্বরূপ, উমাইয়াহ্ শাসনামলের শেষ দিকে হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন (রহ্ঃ)-এর পুত্র ও হযরত ইমাম বাক্বের (রহ্ঃ)-এর ভ্রাতা হযরত ইমাম যায়দ (রহ্ঃ) স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলে হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ) তাঁকে ‘সত্যিকারের ইমাম’ (ইমামে হাক্ব) বলে ঘোষণা করেন এবং এ জিহাদে অংশগ্রহণের জন্যে লোকদেরকে উৎসাহিত করেন। এছাড়া তিনি এ জিহাদে হযরত ইমাম যায়দ (রহ্ঃ)-কে দশ হাজার র্দেহাম আর্থিক সাহায্য দেন এবং বলেন যে, তাঁর নিকট লোকদের বহু আমানত না থাকলে তিনি এ জিহাদে সশরীরে অংশগ্রহণ করতেন। এছাড়া পরবর্তীকালে হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর বংশধর হযরত ইমাম মুহাম্মাদ নাফ্সে যাকীয়্যাহ্ (রহ্ঃ) ও হযরত ইমাম ইবরাহীম (রহ্ঃ)দুই ভাই ‘আব্বাসী স্বৈরশাসক মান্ছূরের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলে হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ) এ জিহাদের পক্ষে ফতোয়া দেন ও এতে অংশগ্রহণের জন্যে লোকদেরকে উৎসাহিত করেন। বিশেষ করে মান্ছূরের একজন সেনাপতি পর্যন্ত হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ)-এর নির্দেশে উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানান।
অনুরূপভাবে হযরত ইমাম মালেক (রহ্ঃ)ও ‘আব্বাসী স্বৈরশাসক মান্ছূরের বিরুদ্ধে হযরত ইমাম মুহাম্মাদ নাফ্সে যাকীয়্যাহ্ (রহ্ঃ) ও হযরত ইমাম ইবরাহীম (রহ্ঃ) ঘোষিত জিহাদকে সমর্থন করে ফতোয়া দেন। শুধু তা-ই নয়, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এ দুই ব্যক্তিত্বের জিহাদের যথার্থতা জানা সত্ত্বেও মান্ছূরের অনুকূলে ইতিপূর্বে কৃত বাই‘আত্ ভঙ্গ করা জায়েয হবে কিনা এ ব্যাপারে অনেকের মনে সংশয় দেখা দিলে তাঁরা যখন হযরত ইমাম মালেক (রহ্ঃ)-এর মত জানতে চান তখন তিনি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত ফয়সালার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন ঃ “যাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য করা হয়েছে তার জন্যে অঙ্গীকার নেই।” অর্থাৎ বলপ্রয়োগ বা চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে যে বাই‘আত্ আদায় করা হয়েছে অথবা ভয়ের কারণে লোকেরা যে বাই‘আত করেছে তা আদৌ বাই‘আত নয়, অতএব, তা রক্ষা করা অপরিহার্য নয় এবং তা ভঙ্গ করলে গুনাহ্ হবে না। তাঁর এ ফতোয়ার ভিত্তিতে বহু লোক মান্ছূরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ইমাম নাফ্সে যাকীয়্যাহ্ (রহ্ঃ)-এর সাথে জিহাদে যোগদান করেন। এ ফতোয়া দেয়ার কারণে ইমাম মালেক (রহ্ঃ)কে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁর শরীর থেকে পোশাক খুলে নিয়ে তাঁকে চাবূক মারা হয়। এর ফলে কাঁধ থেকে তাঁর হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ নির্যাতনের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর স্বাস্থ্যের দারুণ অবনতি ঘটে এবং পরে এরই প্রতিক্রিয়ায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।
এ থেকে সুস্পষ্ট যে, হযরত ইমাম বাক্বের (রহ্ঃ) বা হযরত ইমাম জা‘ফর ছাদেক্ব (রহ্ঃ) ক্ষমতাসীন স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দিলে ও হুকুমতের ওপর স্বীয় দাবী উপস্থাপন করলে হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ) ও হযরতে ইমাম মাালেক (রহ্ঃ) একইভাবে তা সমর্থন করতেন, যদিও হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ)-এর পরবর্তী আহলে বাইতের ইমামগণ হুকুমতের ওপর স্বীয় অধিকারের প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় বাছ¡ীরাত্ দ্বারা পর্যালোচনা করে নিজ নিজ সমকালীন পরিস্থিতিকে বিপ্লবের পতাকা উত্তোলনের জন্য উপযোগী মনে করেন নি এবং সশস্ত্র যুদ্ধকে তখনকার পরিবেশে ইসলামের স্বার্থের জন্য সহায়ক গণ্য করেন নি বলে জিহাদ ঘোষণা করেন নি।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ) ও হযরত ইমাম মালেক (রহ্ঃ) সহ আহলে সুন্নাতের দ্বীনী মনীষীগণ আহলে বাইত্ সম্পর্কে, বিশেষ করে আহলে বাইতের ইমামগণ সম্পর্কে স্বীয় কথা ও কাজে যে সম্মান, সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন তা কী প্রমাণ করে? তাঁরা কি সংশ্লিষ্ট হাদীছগুলোর ভিত্তিতে তাঁদেরকে ‘আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ইমাম’ বলে গণ্য করতেন, কিন্তু সমকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা না করাকেই কল্যাণকর বিবেচনা করেছিলেন? নাকি এ ব্যাপারে অকাট্য ‘আক্বীদায় উপনীত হতে না পারলেও এমনটি হবার সম্ভাবনায় ‘সতর্কতার নীতি’ অনুযায়ী তাঁদের প্রতি সম্মান, সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছিলেন?
এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন।
প্রথমতঃ বিশেষ করে হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ) ও হযরত ইমাম মালেক (রহ্ঃ) ফিক্বহী বিষয়াদিতে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করলেও কোনো মাযহাবের প্রচলন করে যান নি। বরং পরবর্তীকালে তাঁদের নামে মাযহাবের প্রচলন করা হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে মুসলমানদের বিভক্ত করা হয়েছে।
দ্বিতীয়তঃ তাঁরা তাঁদের সমসাময়িক রাজতান্ত্রিক স্বৈরাচারী সরকারগুলোর বিরোধী ছিলেন এবং তাদের সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানান যে কারণে তাঁদেরকে নির্যাতনের শিকার হতে হয় [বিশেষ করে হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ)কে কারাগারে নিক্ষেপ করে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। অন্যদিকে, ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, শারীরিক নির্যাতনের প্রতিক্রিয়ায় হযরত ইমাম মালেক (রহ্ঃ)-এর মৃত্যু ঘটে।], কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁদের নামে মাযহাবের প্রচলন করে স্বৈরাচারী সরকারগুলোর সাথে সহযোগিতা করা হয়, আর আহলে বাইতের ইমামগণের সাথে ক্ষমতাসীনদের দুশমনীর প্রেক্ষাপটে দলীয় অনুভূতি ও শিয়া-সুন্নী পার্থক্য ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে।
তৃতীয়তঃ বহুলাংশে সরকারের সাথে সহযোগিতার প্রভাবেই পরবর্তীকালে হানাফী মাযহাবে হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ)-এর কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়া থেকে সরে এসে নতুন ফতোয়া দেয়া হয় [যার মধ্যে এক বৈঠকে প্রদত্ত তিন তালাককে চূড়ান্ত তালাক বলে গণ্যকরণ অন্যতম, অথচ হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ) একে এক তালাক বলে গণ্য করতেন।] যা ফিক্বহী বিষয়াদিতে শিয়া-সুন্নী পার্থক্যকে ব্যাপকতর করে তোলে।
চতুর্থতঃ একান্তই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আহলে বাইতের ইমামগণের অনুসারীদেরকে সুন্নাতে রাসূল (সাঃ)-এর অনুসারী নয় বলে জনমনে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে “আহলে সুন্নাত্ ওয়াল্ জামা‘আত্” নাম তৈরী করে সে নামে নিজেদেরকে অভিহিত করা হয়।
পঞ্চমতঃ “ছিহাহ্ সিত্তাহ্” [বলা বাহুল্য যে, এ বিশেষণটিও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। কারণ, বিচারবুদ্ধির অকাট্য রায় অনুযায়ী বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে স্তরসংখ্যা যত বেশী হবে তথ্যবিকৃতির আশঙ্কাও তত বেশী থাকে এবং স্তরসংখ্যা যত কম হবে নির্ভরযোগ্যতার সম্ভাবনাও তত বেশী হবে। এ কারণেই সুন্নী ধারার হাদীছ-গ্রন্থাবলীর মধ্যে হযরত ইমাম মালেক (রহ্ঃ) কর্তৃক সংকলিত “মুওয়াত্বা”য় ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্বলতার আশঙ্কা কম ছিলো। [তাই হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহ্লাভী (রহ্ঃ) “মুওয়াত্বা”কে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য হাদীছ-গ্রন্থ বলে গণ্য করতেন।] কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে “মুওয়াত্বা”কে “ছহীহ্ নয়” বলে জনমনে ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরবর্তী কালে ছয়টি হাদীছ-সংকলনকে “ছি¡হাহ্ সিত্তাহ্” (ছয়টি ছহীহ্) বলে চিহ্নিত করা হয়, যদিও সেগুলো “মুওয়াত্বত্বা” সংকলনের শতাব্দী কালেরও বেশী পরে সংকলিত হয়।]নামে পরিচিত হাদীছ-গ্রন্থ সমূহ সহ আহলে সুন্নাতের অন্যান্য হাদীছ-গ্রন্থ হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ) ও হযরত ইমাম মালেক (রহ্ঃ)-এর শতাব্দীকাল পরে বা তারও বেশী পরে সংকলিত হলেও সেগুলোকে গ্রহণ করার ফলে শিয়া-সুন্নী ব্যবধান আরো বেশী ব্যাপকতা লাভ করে। বিশেষ করে হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ) যেখানে ফিক্বহী ব্যাপারে খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছকে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করতেন না , [এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, উমাইয়াহ্ ও ‘আব্বাসী যুগে অসংখ্য জাল হাদীছ রচিত হওয়া এবং হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ওফাতের শতাব্দীকালেরও বেশী সময় পরে অনেকগুলো স্তরের নামে বর্ণিত খবরে ওয়াহেদ্ জাল ও ছহীহ্ হাদীছের মধ্যে নিশ্চিতভাবে পার্থক্য করতে পারা ‘অসম্ভব’ না হলেও ‘প্রায় অসম্ভব’ ছিলো, বিশেষ করে হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ) তা অসম্ভব মনে করতেন বলেই তা গ্রহণ করেন নি। এ থেকে আরো শতাব্দীকাল পরে সংগৃহীত হাদীছ সমূহের অবস্থা অনুমান করা যেতে পারে। বস্তুতঃ মুসলমানদের মধ্যে মাযহাবী বিষয়াদির ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের সিংহ ভাগের জন্যই জাল হাদীছ দায়ী।] সেখানে পরবর্তীকালে খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছ ব্যাপকভাবে গ্রহণের ফলে বিশেষ করে হানাফী মাযহাবের চেহারা অনেক বেশী পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যে পার্থক্য তীব্রতর হয়ে ওঠে। [এ প্রসঙ্গে পুনরায় উল্লেখ করতে হয় যে, খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছকে চোখ বুঁজে প্রত্যাখ্যান করা ঠিক নয়, বরং ইসলামের চারটি অকাট্য জ্ঞানসূত্র গ্রহণের পরে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সে সবের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়ার শর্তে খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছ গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে এটা অনস্বীকার্য যে, চার অকাট্য জ্ঞানসূত্র গ্রহণ করার পর কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নই জবাব বিহীন থাকে না; কেবল কতক গৌণ ও খুটিনাটি বিষয় অবশিষ্ট থাকে। আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে, আজকের দিনে উক্ত চার জ্ঞানসূত্রের ব্যবহার ও তার ভিত্তিতে খবরে ওয়াাহেদ্ হাদীছ পরীক্ষা করা যতখানি সহজ তৎকালে তা অত সহজ ছিলো না।
এ প্রসঙ্গেই আরো উল্লেখ করতে হয় যে, অনেক পরবর্তীকালে আহলে সুন্নাতের ধারাবাহিকতায় উদ্ভূত “আহলে হাদীছ” নামক ফির্ক্বাহর অনুসারীদের অনেকে হানাফীদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কথা মানে না, আবূ হানীফাহ্ কথা মানে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কথা বলে দাবীকৃত কথা ও প্রকৃতই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কথা কখনোই এক নয় এবং ইমাম বুখারী সহ হাদীছ সংকলকগণের বিচারক্ষমতার ওপরে অন্ধভাবে আস্থা পোষণের পক্ষে কোনো দলীল নেই, বিশেষ করে তাঁরা যখন না মা‘ছূম ছিলেন, না অকাট্যভাবে ঐশী ইল্হামের অধিকারী ছিলেন, না রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকটবর্তী কালের ছিলেন, বরং তাঁদেরকে হাদীছের ব্যাপারে অনেকগুলো স্তরের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিলো যেগুলোর গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে তাঁদের পক্ষে শতকরা একশ’ ভাগ নিশ্চিত হওয়া সম্ভব ছিলো না।]ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওল্টানো কেন
অনেককেই ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসের বিরোধ-বিসম্বাদ সংক্রান্ত পৃষ্ঠাগুলো ওল্টানোর বিরোধিতা করতে দেখা যায়। তাঁদের মতে, এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান বিভেদ-অনৈক্যই কেবল বৃদ্ধি পাবে এবং তা ফির্ক্বাহ্ ও মাযহাবের উর্ধে উঠে বৃহত্তর ইসলামী ঐক্য গড়ে তোলার বিষয়টিকে সুদূরপরাহত করে তুলবে।
আসলেও ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগের তিক্ত বিষয়গুলোর স্মৃতিচারণ না করাই ভালো। প্রথমতঃ এর সাথে যারা জড়িত তাঁদের কেউই বেঁচে নেই এবং এখন ইতিহাসকে বদলে দেয়া যাবে না। আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমল সহকারে আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে হাযির হবেন। আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীন যেমন এরশাদ করেছেন ঃ
تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
“তারা ছিলো একটি জনগোষ্ঠী যারা অতীত হয়ে গিয়েছে; তারা (ভালো) যা কিছু অর্জন করেছে তা তাদেরই জন্য এবং তারা (মন্দ) যা কিছু অর্জন করেছে তা তাদেরই ওপরে আপতিত হবে। আর তারা যা কিছু করেছে সে জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।” (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ ঃ ১৩৪)
দ্বিতীয়তঃ শিয়া মাযহাবের অনুসারীরা যে বারো জন বুযুর্গ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে মনোনীত ইমাম বলে ‘আক্বীদাহ্ পোষণ করে তাঁদের মধ্য থেকে এগারো জন এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যকার দ্বাদশ ইমাম Ñ শিয়া মাযহাবের অনুসারীরা যাকে ইমাম মাহ্দী (আঃ) বলে ‘আক্বীদাহ্ পোষণ করে, তাদের ‘আক্বীদাহ্ অনুযায়ীই আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁকে দীর্ঘজীবী করলেও তিনি আল্লাহর ইচ্ছায়ই আত্মপরিচয় গোপন করে আছেন এবং উপযুক্ত সময়ে আত্মপ্রকাশ করবেন।
যেহেতু শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে সকল মুসলমানই হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আবির্ভাব ও তাঁর দ্বারা বিশ্বব্যাপী ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ‘আক্বীদাহ্ পোষণ করে, সেহেতু তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন কি করেন নি এ প্রশ্নে মতপার্থক্য থাকলেও তাঁর আত্মপ্রকাশের পর তাঁকে গ্রহণ-বর্জনের ওপরই যে কারো হেদায়াত ও গোমরাহী নির্ভর করবে। কিন্তু এখন যেহেতু উক্ত বারো জন বুযুর্গ ব্যক্তির কেউই আমাদের সামনে ইমামতের দাবী নিয়ে উপস্থিত নন, এমতাবস্থায় তাঁদের ইমামত নিয়ে বিতর্ক একটি তাত্ত্বিক বিতর্ক বৈ নয় এবং এ থেকে কোনোই বাস্তব ফায়দা পাওয়া যাবে না, বরং এ বিতর্কের ফলে মুসলমানদের মধ্যকার বিভেদ-অনৈক্যই বৃদ্ধি পাবে।
এ ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই যে, আসলেই আমাদের উচিত অতীত হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের আমলের সাথে নিজেদেরকে না জড়ানো। কারণ, আমাদের বিতর্ক তাঁদের আমলের ভালো-মন্দ কোনো কিছুতেই কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাতে পারবে না। কিন্তু আমরা যখন নিজেদেরকে তাঁদের ‘আমলের সাথে জড়িয়ে ফেলি তখন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের ‘আমলের পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।
বিশেষ করে অনেক সময় বলা হয় যে, অন্যান্য ছাহাবায়ে কেরাম ও অতীতের মনীষীগণ ইসলাম সম্পর্কে ও কোরআন মজীদের তাৎপর্য আমাদের চেয়ে কম বুঝতেন না। অথচ এটা অনস্বীকার্য যে, তাঁরা না মা‘ছূম ছিলেন, না অকাট্যভাবে ঐশী ইল্হামের অধিকারী ছিলেন। অতএব, তাঁদের পক্ষে ভুল করা সম্ভব এবং পূর্বোল্লিখিত আয়াত অনুযায়ী, তাঁরা ভুল করে থাকলে আমাদের জন্য তার অনুসরণ করা উচিত হবে না। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের কথা ও কাজের বর্ণনা কতখানি সঠিকভাবে আমাদের কাছে পৌঁছেছে তা-ও প্রশ্নের উর্ধে নয়।
আরো বলা হয় যে, আমরা তো কোরআন মজীদ ও ইসলাম ছাহাবীদের মাধ্যমেই পেয়েছি, সুতরাং তাঁদেরকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না।
কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, আমরা কোরআন ও ইসলাম তাঁদের ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে পাই নি, বরং মুতাওয়াতির সূত্রে ‘তাঁদের সকলের কাছ থেকে’ পেয়েছি যার নির্ভুলতা ও গ্রহণযোগ্যতা সন্দেহাতীত। এর সাথে যে সব বিষয়ে তাঁদের নিজেদের মধ্যেই পারস্পরিক মতপার্থক্য ছিলো সে সব বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদেরকে নির্ভুল গণ্য করা ঠিক হবে না। আর ইসলাম ও কোরআনকে পরবর্তী প্রজন্মসমূহের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন বলেই যে তাঁরা তা পরবর্তী প্রজন্ম সমূহের তুলনায় অধিকতর সঠিকভাবে বুঝেছিলেন এমনটি মনে করার কোনো কারণ নেই। কেননা, হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, জ্ঞানপূর্ণ কথা অনেক সময় কেউ এমন ব্যক্তির কাছে বহন করে নিয়ে যায় যে বহনকারীর তুলনায় অধিকতর সমঝদার। [হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্‘উদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ
نَضَّرَ الله عَبداً سَمِعَ مَقالَتی فَحَفِظَها و وَعاها وَاَدَّها کَما سَمِعَها فَرُبَّ مُبَلّغٍ اَوعی لَها مِن سامِعٍ.
“আল্লাহ্ চিরসতেজ করে রাখুন (তাঁর) সেই বান্দাহ্কে যে আমার কথা শুনলো, অতঃপর তা সংরক্ষণ করে রাখলো ও স্মরণ রাখলো এবং তা যেভাবে শুনলো হুবহু সেভাবেই (অন্যের কাছে) পৌঁছে দিলো; আর অনেক সময় এমন হয় যে, (পরোক্ষভাবে) যার কাছে তা পৌঁছেছে সে তা (আমার কাছ থেকে) শ্রবণকারীর তুলনায় উত্তমরূপে গ্রহণ করেছে।” (আবূ দাউদ; তিরমিযী)
বাংলাদেশে (এবং হয়তো আরো কোথাও কোথাও) অনেক লোক রাগের মাথায় স্ত্রীকে এক বৈঠকে ‘তিন তালাক্ব’ দেয়ার পর জীবনের প্রয়োজনে, বিশেষতঃ সন্তানদের কারণে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ‘হীলা’র (যা একটি ফার্সী শব্দ যার মানে ‘প্রতারণা’) আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। যেহেতু চূড়ান্ত তালাক্বের পর তালাক্বপ্রাপ্তা স্ত্রী অন্য কোনো পুরুষের সাথে স্থায়ীভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার ও সে স্বামীর মৃত্যু ঘটা বা সে স্বামী কর্তৃক তালাক্বপ্রাপ্তা হওয়ার পূর্বে প্রথম স্বামীর জন্য তাকে বিবাহ করার সুযোগ নেই এবং যেহেতু নতুন স্বামীর মৃত্যু ঘটা বা তার পক্ষ থেকে ঐ স্ত্রীকে তালাক্ব দেয়ার কোনোই নিশ্চয়তা থাকে না সেহেতু এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে আপোসে কোনো ব্যক্তিকে এ শর্তে ঐ নারীকে বিবাহ করার জন্য রাযী করানো হয় যে, বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী মাত্র এক রাতের জন্য একত্রবাস করার পরই নতুন স্বামী তাকে তালাক্ব দেবে।
বলা বাহুল্য যে, এ ধরনের বিবাহ ইসলামের কোনো মাযহাবের দৃষ্টিতেই ছহীহ্ নয়। কারণ, প্রকাশ্য বা গোপন যে কোনোভাবেই হোক না কেন তালাক্ব দেয়ার পূর্বশর্ত বিশিষ্ট বিবাহ ইসলামসম্মত কোনো বিবাহের আওতায় পড়ে না। এ ধরনের বিবাহ না স্থায়ী বিবাহ, না অস্থায়ী বিবাহ। ইসলামের সকল ফির্ক্বাহ্ ও মাযহাবের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে তালাক্বপ্রাপ্তা নারী কেবল স্থায়ী বিবাহের পরেই এ স্বামীর মৃত্যু বা তালাক্বের পরে পূর্ববর্তী স্বামীর সাথে পুনর্বিবাহিত হতে পারবে। এমতাবস্থায় স্থায়ী বিবাহ হিসেবে পাতানো এই তথাকথিত বিবাহ সুস্পষ্টতঃই ব্যভিচার বৈ নয়। কারণ, যেহেতু অস্থায়ী বিবাহের ক্ষেত্রে অস্থায়ী হিসেবেই ও মেয়াদ নির্দিষ্ট করে ‘আক্বদ্ পড়ানো হয় এবং মেয়াদশেষে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বিবাহের সমাপ্তি ঘটে; তালাক্ব দেয়ার প্রয়োজন হয় না সেহেতু এ ধরনের পাতানো বিবাহ ‘অস্থায়ী বিবাহ’ও নয়।
অন্যদিকে যারা এ ধরনের হীলা (প্রতারণা)র ঘৃণ্য নাজায়েয কাজ হওয়ার কারণে এর আশ্রয় গ্রহণ করে না প্রচলিত ফতোয়ার কারণে তারা তালাক্ব দেয়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারে না, ফলে অনেক সময় তাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের ওপর অন্ধকার নেমে আসে Ñ যা আল্লাহ্ তা‘আলার পসন্দনীয় নয় বলেই তিনি দু’-দুই বার তালাক্বের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার সুযোগ দিয়েছেন।]বস্তুতঃ আমরা যদি বিচারবুদ্ধির কাছে গ্রহণযোগ্য ইসলামের সর্বজনগ্রহণযোগ্য চারটি অকাট্য সূত্রের ওপর নির্ভর করে তার দাবী অনুযায়ী আমাদের জীবনে সকল ক্ষেত্রে চলার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মনীতি ও বিধিবিধান লাভের ও তদনুযায়ী চলার চেষ্টা করতাম তাহলে উপরোল্লিখিত ঐতিহাসিক বিতর্ক এমনিতেই গুরুত্ব হারিয়ে ফেলতো। কিন্তু আমরা তা না করার কারণেই এ বিতর্কের উপযোগিতা থেকে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। কারণ, বিচারবুদ্ধি (‘আক্বল্), কোরআন মজীদ, মুতাওয়াতির হাদীছ ও ইজ্মা ‘এ উম্মাহর মানদণ্ডে যেখানে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর আহলে বাইতের পবিত্রতা ও পাপমুক্ততা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় এবং জ্ঞানগত যোগ্যতার সাথে পবিত্রতা ও পাপমুক্ততা যুক্ত হওয়ার কারণে কেবল তাঁদের কাছ থেকেই নির্ভুল দ্বীনী জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে এমতাবস্থায় আমরা যদি অন্য কারো কাছ থেকে এ সব মানদণ্ডের কোনো না কোনোটির সাথে সাংঘর্ষিক কোনো ফয়সালা মেনে না চলতাম এবং তার ওপরে একগুঁয়েমি না করতাম তাহলে আজ আর ইতিহাস পর্যালোচনার প্রয়োজন হতো না।
উদাহরণ স্বরূপ এক বৈঠকে তিন তালাক সংক্রান্ত ফতোয়ার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
আল্লাহ্ তা‘আলা যেখানে ফেরতযোগ্য তালাক্ব (طلاق رجعی) সম্পর্কে এরশাদ করেছেন যে, الطلاق مرتان. তালাক্ব দুই বার (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ ঃ ২২৯) অতঃপর ভালোভাবে রাখতে হবে অথবা (তৃতীয় দফা তালাক্ব দিয়ে) ভদ্রভাবে বিদায় করে দিতে হবে (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ ঃ ২২৯) এমতাবস্থায় কেউ যে কোনো কথা বলেই (যেমন ঃ ‘তিন তালাক্ব’ শব্দ উচ্চারণ করে বা ‘তালাক্ব’ শব্দটি তিন বার পুনরাবৃত্তি করে) স্ত্রীকে তালাক্ব দি’ক না কেন অবশ্যই তা ‘এক বার’ তালাক্ব হবে, অতঃপর তাকে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত তার পক্ষে ঐ স্ত্রীকে দ্বিতীয় বার তালাক্ব দেয়া সম্ভব নয়। কারণ, প্রথম বার তালাক্ব দেয়ার সাথে সাথেই সে আর তার স্ত্রী থাকলো না এবং যে সব কাজের দ্বারা ‘তালাক্ব দেয়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা’ প্রমাণিত হয় এমন কোনো কাজের মাধ্যমে তাকে ফিরিয়ে এনে স্ত্রীর মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার আগে তাকে ‘দ্বিতীয় বার’ তালাক্ব দেয়া সম্ভব নয়।
কিন্তু এ সত্ত্বেও কেবল দ্বিতীয় খলীফাহর মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে মুসলমানদের মধ্যকার বৃহত্তর অংশের মধ্যে এক বৈঠকে প্রদত্ত ‘তিন তালাক্ব’কে ফেরত-অযোগ্য চূড়ান্ত তালাক্ব বলে গণ্য করা হচ্ছে।
এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, স্বয়ং হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ)যার নামে হানাফী মায্হাবের প্রচলন করা হয়েছে যেখানে এক বৈঠকে প্রদত্ত ‘তিন তালাক্ব’কে ফেরতযোগ্য ‘এক বার’ তালাক্ব বলে গণ্য করতেন সেখানে পরবর্তীকালে গৃহীত ‘হানাফী মাযহাবের মত’ হচ্ছে এই যে, এক বৈঠকে প্রদত্ত ‘তিন তালাক্ব’ ফেরত-অযোগ্য চূড়ান্ত তালাক্ব বলে গণ্য হবে। আর এর ফলে যে কেবল আল্লাহর বিধানে মানুষের জীবনের জন্য প্রদত্ত প্রশস্ততা ও সহজতা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে শুধু তা-ই নয়, বরং অনেককে কঠিন ধরনের গুনাহে লিপ্ত হবার পথে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। [বাংলাদেশে (এবং হয়তো আরো কোথাও কোথাও) অনেক লোক রাগের মাথায় স্ত্রীকে এক বৈঠকে ‘তিন তালাক্ব’ দেয়ার পর জীবনের প্রয়োজনে, বিশেষতঃ সন্তানদের কারণে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ‘হীলা’র (যা একটি ফার্সী শব্দ Ñ যার মানে ‘প্রতারণা’) আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। যেহেতু চূড়ান্ত তালাক্বের পর তালাক্বপ্রাপ্তা স্ত্রী অন্য কোনো পুরুষের সাথে স্থায়ীভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার ও সে স্বামীর মৃত্যু ঘটা বা সে স্বামী কর্তৃক তালাক্বপ্রাপ্তা হওয়ার পূর্বে প্রথম স্বামীর জন্য তাকে বিবাহ করার সুযোগ নেই এবং যেহেতু নতুন স্বামীর মৃত্যু ঘটা বা তার পক্ষ থেকে ঐ স্ত্রীকে তালাক্ব দেয়ার কোনোই নিশ্চয়তা থাকে না সেহেতু এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে আপোসে কোনো ব্যক্তিকে এ শর্তে ঐ নারীকে বিবাহ করার জন্য রাযী করানো হয় যে, বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী মাত্র এক রাতের জন্য একত্রবাস করার পরই নতুন স্বামী তাকে তালাক্ব দেবে।
বলা বাহুল্য যে, এ ধরনের বিবাহ ইসলামের কোনো মাযহাবের দৃষ্টিতেই ছহীহ্ নয়। কারণ, প্রকাশ্য বা গোপন যে কোনোভাবেই হোক না কেন তালাক্ব দেয়ার পূর্বশর্ত বিশিষ্ট বিবাহ ইসলামসম্মত কোনো বিবাহের আওতায় পড়ে না। এ ধরনের বিবাহ না স্থায়ী বিবাহ, না অস্থায়ী বিবাহ। ইসলামের সকল ফির্ক্বাহ্ ও মাযহাবের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে তালাক্বপ্রাপ্তা নারী কেবল স্থায়ী বিবাহের পরেই এ স্বামীর মৃত্যু বা তালাক্বের পরে পূর্ববর্তী স্বামীর সাথে পুনর্বিবাহিত হতে পারবে। এমতাবস্থায় স্থায়ী বিবাহ হিসেবে পাতানো এই তথাকথিত বিবাহ সুস্পষ্টতঃই ব্যভিচার বৈ নয়। কারণ, যেহেতু অস্থায়ী বিবাহের ক্ষেত্রে অস্থায়ী হিসেবেই ও মেয়াদ নির্দিষ্ট করে ‘আক্বদ্ পড়ানো হয় এবং মেয়াদশেষে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বিবাহের সমাপ্তি ঘটে; তালাক্ব দেয়ার প্রয়োজন হয় না সেহেতু এ ধরনের পাতানো বিবাহ ‘অস্থায়ী বিবাহ’ও নয়।
অন্যদিকে যারা এ ধরনের হীলা (প্রতারণা)র ঘৃণ্য নাজায়েয কাজ হওয়ার কারণে এর আশ্রয় গ্রহণ করে না প্রচলিত ফতোয়ার কারণে তারা তালাক্ব দেয়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারে না, ফলে অনেক সময় তাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের ওপর অন্ধকার নেমে আসে Ñ যা আল্লাহ্ তা‘আলার পসন্দনীয় নয় বলেই তিনি দু’-দুই বার তালাক্বের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার সুযোগ দিয়েছেন।]এখানে মাত্র একটি দৃষ্টান্ত দেয়া হলো। এ ধরনের আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। এভাবে অনেক ছাহাবীর যাদের নিষ্পাপ হওয়ার সপক্ষে কোনোই দলীল নেই মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে এ ধরনের আরো অনেক ভ্রান্ত ফতোয়া দেয়া হয়েছে যা মুসলমানদের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধির কারণ হয়েছে।
আজকের করণীয়
ইসলামের দৃষ্টিতে আজকের দিনে মুসলমানদের দ্বীনী সমস্যাবলীকে তিনটি সমস্যার মধ্যে সমন্বিত করা যায়; তাদের অন্যান্য পার্থিব ও অপার্থিব সমস্যাবলী এ তিনটির কোনোটি না কোনোটির আওতাভুক্ত এবং উক্ত তিনটি সমস্যার সমাধান হলে অন্যান্য সমস্যার সমাধানও খুব সহজেই সম্ভব হবে। এ তিনটি সমস্যা হচ্ছে ‘আক্বায়েদের সমস্যা, ফিক্বহী সমস্যা এবং নেতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্বের সমস্যা।
ইসলাম তার মৌলিক ‘আক্বায়েদের (اصول دين) ক্ষেত্রে কোনোরূপ অন্ধ বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেয় নি যা বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ্কে গ্রাস করে নিয়েছে। বরং ইসলাম তার মৌলিক ‘আক্বায়েদের তিনটি বিষয়কে অর্থাৎ তাওহীদ, আখেরাত ও রিসালাত্কে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সমানভাবে গ্রহণীয় সর্বজনীন মানদণ্ড বিচারবুদ্ধি (عقل)-এর ওপর ভিত্তিশীল করেছে যাতে কারো জন্য নিজ নিজ অন্ধ বিশ্বাসের ওপর অটল থাকার পক্ষে কোনো দলীল না থাকে।
আল্লাহ্ তা‘আলা কোরআন মজীদে বার বার ‘আক্বল্-এর আশ্রয় গ্রহণের জন্য সকল মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এবং যারা ‘আক্বল্-এর আশ্রয় গ্রহণ করে না তাদেরকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। আল্লাহ্ তা‘আলা স্বীয় অস্তিত্ব ও তাওহীদ, আখেরাত এবং নবুওয়াতে মুহাম্মাদী (সাঃ) ও কোরআন মজীদের ঐশী গ্রন্থ হওয়ার সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। অতএব, মুসলমানদেরকে ইসলামের উছূলে ‘আক্বায়েদকে ‘আক্বলী দলীলের ভিত্তিতে নতুন করে জানতে ও গ্রহণ করতে হবে এবং অমুসলিমদেরকে এরই ভিত্তিতে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে হবে।
অতঃপর ‘আক্বায়েদের বিস্তারিত বিষয়াদির ক্ষেত্রে কোরআন মজীদকে ও তার সহায়ক ব্যাখ্যাকারী শক্তি হিসেবে ‘আক্বল্-কে এবং মুতাওয়াতির হাদীছ সমূহ ও ইজ্মা ‘এ উম্মাহ্কে (কোনো ফির্ক্বাহ্ বা মাযহাব বিশেষের ইজ্মা ‘কে নয়) গ্রহণ করতে হবে। হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সর্বশেষ নবী হওয়া, কোরআন মজীদের সর্বশেষ এবং একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও সংরক্ষিত ঐশী কিতাব হওয়া, আর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর স্থলাভিষিক্ততার বিষয়গুলো এ সব সূত্র থেকেই অকাট্যভাবে পাওয়া যায়।
বলা বাহুল্য যে, মূল ও গুরুত্বপূর্ণ ফিক্বহী জিজ্ঞাসাবলীর জবাব উপরোক্ত চারটি মৌলিক দ্বীনী সূত্র থেকেই পাওয়া যায়। এ লক্ষ্যে ইজতিহাদকে অব্যাহত রাখতে হবে এবং যে সব ফির্ক্বাহ্ ও মাযহাব ইজতিহাদের দরযা বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে মনে করে তাদেরকে সে দরযা পুনরায় খুলে দিতে হবে। কারণ, ইসলামে ইজতিহাদের বৈধতা থাকলে যার বৈধতার ব্যাপারে সকলেই একমত তার দরযা কেউ কখনো বন্ধ করতে পারে না। বিশেষ করে কোরআন মজীদের নিুোক্ত আয়াত থেকে মুসলিম সমাজে ইজতিহাদের অস্তিত্ব থাকা ফরযে কেফায়ী হিসেবে প্রমাণিত হয়।
আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ করেন ঃ
فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
“কেন এমন হলো না যে, তাদের (মু’মিনদের) প্রতিটি গোষ্ঠীর মধ্য থেকে কতক লোক বেরিয়ে পড়বে এবং দ্বীনের গভীর সমঝ অর্জনের পর যখন স্বীয় কওমের কাছে ফিরে যাবে তখন তাদেরকে সতর্ক করবে যাতে তারা (আল্লাহর ) নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকে।” (সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্ ঃ ১২২)
অন্যদিকে যাদের মধ্যে ইজতিহাদ অব্যাহত রয়েছে তাদেরকে পূর্ব থেকে চলে আসা ইজতিহাদের মূলনীতি ও জ্ঞানসূত্রসমূহ সম্পর্কে সব সময়ই এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ছাহাবীগণ সহ অতীতের মনীষীগণের মধ্যেও ভুল ও দুর্বলতা থাকতে পারে। বিশেষ করে তাঁদের কারো কোনো মত যদি কোরআন মজীদের কোনো আয়াতের সাথে বা হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর মত বলে ইয়াক্বীন সৃষ্টি হয় এমন কোনো মতের সাথে সাংঘর্ষিক হয় সে ক্ষেত্রে কিছুতেই তাঁর সে মত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।
এখানে আরো উল্লেখ্য যে, ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ক্বিয়াস্ নিয়ে বিতর্ক আছে। এ প্রসঙ্গে অনস্বীকার্য যে, কোরআন ও সুন্নাতে রাসূল (সাঃ)-এর মোকাবিলায় ক্বিয়াস্-এর কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। তবে এর বাইরে ক্বিয়াস্-এর গ্রহণযোগ্যতা আছে কিনা তা স্বতন্ত্রভাবে বিচার্য বিষয়।
প্রকৃত পক্ষে ওপরে যে, চারটি সর্বসম্মত অকাট্য দ্বীনী সূত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাকে চূড়ান্ত ও বিতর্কাতীত সূত্র হিসেবে এবং সেই সাথে এ চার মানদণ্ডের বিচারে উৎসে যাওয়া খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছ সমূহকে পঞ্চম উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হলে এর বাইরে তেমন কোনো দ্বীনী জিজ্ঞাসা থাকতে পারে না।
এমতাবস্থায় মুজতাহিদের কাজ হবে উপরোক্ত সূত্রসমূহ নিয়ে গবেষণা করে নবজাগ্রত বা বিতর্কিত সমস্যাবলী সম্পর্কে আল্লাহ্ ও রাসূলের (সাঃ) ফয়সালা উদ্ঘাটন করা। অতঃপর আর কোনো প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকতে পারে না। এতদ্সত্ত্বেও আমরা যদি ধরে নেই যে, আরো কিছু প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকতে পারে এবং তার সমাধানের জন্য ক্বিয়াসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তো সে সব প্রশ্ন হবে খুবই গৌণ বিষয়াদিতে মুস্তাহাব ও মাক্রূহ্ সংক্রান্ত। এর ফলে ক্বিয়াসের ক্ষেত্র খুবই সীমিত হয়ে আসবে এবং মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ফিক্বহী মতপার্থক্যও প্রায় শূন্যের কাছাকাছি চলে আসবে, অন্ততঃ কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই মতপার্থক্য থাকবে না।
বস্তুতঃ মুসলমানদের মধ্যে যে সব ফিক্বহী মতপার্থক্য রয়েছে তার বেশীর ভাগেরই কারণ হচ্ছে সরাসরি কোরআন মজীদ থেকে ফিক্বহী জিজ্ঞাসাবলীর জবাব সন্ধানে যথাযথ প্রচেষ্টা না চালানো এবং এ ব্যাপারে খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছ ও অতীতের মনীষীদের ওপর অনেক বেশী মাত্রায় এবং অনেক ক্ষেত্রে অন্ধভাবে নির্ভরতা, অথচ হাদীছের রাভীগণ ও সংকলকগণ এবং অতীতের মনীষীগণ না মা‘ছূম ছিলেন, না সরাসরি ঐশী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তা‘আলা যেখানে কোরআন মজীদকে ‘সকল জ্ঞানের আধার’ (تبياناً لکل شيء) বলে উল্লেখ করেছেন সেখানে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ফিক্বহী সমস্যা তথা ফরয ও হারাম সংক্রান্ত কোনো সমস্যাই সমাধান বিহীন থাকতে পারে না।
অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, ‘আক্বায়েদ-কে ওপরে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেভাবে গ্রহণ করার পর কোরআন নিয়ে গভীরভাবে চর্চা করা হলে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ফিক্বহী সমস্যাই সমাধানবিহীন থাকে না। তালাক্ব, অস্থায়ী বিবাহ, ওয়াছীয়্যাত্ ও কোনো কোনো মীরাছী বিষয় সহ যে সব গুরুত্বপূর্ণ ফিক্বহী বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ রয়েছে তার সবগুলোর সমাধানই কোরআন মজীদে নিহিত রয়েছে; ‘আক্বল্, মুতাওয়াতির হাদীছ ও ইজ্মা‘এ উম্মাহ্র সাহায্য নিয়ে এর সবগুলোই উদ্ঘাটন করা সম্ভব।
অবশ্য কোরআন মজীদ থেকে সঠিক তাৎপর্য গ্রহণের ক্ষেত্রে স্থানগত, কালগত, ভাষাগত ও পরিবেশগত ব্যবধানের কারণে যে সব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা কাটিয়ে ওঠা অপরিহার্য এবং তা কাটিয়ে ওঠার জন্য সংশ্লিষ্ট জ্ঞানগবেষক (মুজতাহিদ)গণকে কোরআন নাযিলের যুগের আরবী ভাষার জ্ঞানের সাথে সাথে সঠিক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যকরণে সহায়ক শাস্ত্রসমূহেরও (যেমন ঃ জ্ঞানতত্ত্ব, তাৎপর্যবিজ্ঞান, যুক্তিবিজ্ঞান ও দর্শন) আশ্রয় নিতে হবে।
উপরোক্ত চার মৌলিক সূত্র থেকে ফিক্বহী জিজ্ঞাসাবলীর জবাব সন্ধান করা হলে এরপর মাত্র কতক গৌণ বিষয়ই অবশিষ্ট থাকতে পারে। কারণ, আল্লাহ্ তা‘আলা যে সব উদ্দেশ্যে নবী-রাসূলগণকে (আঃ) প্রেরণ করেন তার মধ্যে সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকদেরকে আল্লাহ্ তা‘আলার সাথে পরিচিত করানো এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে আল্লাহ্ তা‘আলা কর্তৃক নির্ধারিত ফরয ও হারামগুলো সম্বন্ধে জানিয়ে দেয়া। এমতাবস্থায় এটা সম্ভব নয় যে, একজন রাসূল এ সম্পর্কে তাঁর স্বল্পসংখ্যক ছাহাবীকে জানাবেন, বরং এ ধরনের আহ্কাম বিপুল সংখ্যক ছাহাবীর জানা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আর যেহেতু হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ওফাতের সময় তাঁর ছাহাবীর সংখ্যা ছিলো লক্ষাধিক, সুতরাং খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছের দ্বারা ফরয বা হারাম প্রমাণিত হতে পারে না। অবশ্য বিস্তারিত তথা খুটিনাটি, বিশেষতঃ প্রায়োগিক বিধান ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছ গ্রহণযোগ্য, কিন্তু তার গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে উপরোক্ত চার সূত্রের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়ার শর্তে।
বলা বাহুল্য যে, কোরআন মজীদের ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত আহ্কামের ক্ষেত্রে নিষ্পাপ (মা‘ছূম) ব্যক্তিত্ববর্গের কথা ও কাজ নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া মুসলমানদের কর্তব্য, কিন্তু কোনো হাদীছ গ্রন্থে কোনো কিছু মা‘ছূমের কথা বা কাজ হিসেবে উল্লেখ থাকা মানেই যে সত্যি সত্যিই তা মা‘ছূমের কথা ও কাজ এটা নিশ্চিত করে বলা চলে না। বরং একজন মুজতাহিদ যে কোনো খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছকে উপরোক্ত চার দলীলের মানদণ্ডে ও হাদীছ বিচারের আরো বহু মানদণ্ডে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যখন এ প্রত্যয়ে উপনীত হবেন যে, তা সত্যি সত্যিই মা‘ছূমের কথা বা কাজ কেবল তখনি তিনি তা গ্রহণ করবেন।
এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় হচ্ছে এই যে, কোনো হাদীছের ক্ষেত্রে মা‘ছূম ও হাদীছ-সংকলকের মাঝে বর্ণনাস্তরের (রাভী) সংখ্যা যত কম হবে হাদীছে ভ্রান্তি বা বিকৃতি প্রবেশ বা পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা ততটা কম এবং বর্ণনাস্তরের আধিক্যের ক্ষেত্রে ভ্রান্তি, বিকৃতি ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা তত বেশী। মোদ্দা কথা, শিয়া ও সুন্নী নির্বিশেষে কোনো ধারার কোনো হাদীছ-গ্রন্থেরই সকল হাদীছকে চোখ বুঁজে গ্রহণ বা চোখ বুঁজে প্রত্যাখ্যান করার উপায় নেই।
বস্তুতঃ ‘আক্বায়েদী ও ফিক্বহী উভয় ক্ষেত্রেই শিয়া-সুন্নী দুস্তর ব্যবধান গড়ে ওঠার অন্যতম কারণ হচ্ছে হয় ইজতিহাদকে অবৈধ গণ্য করা, নয়তো বৈধ গণ্য করা সত্ত্বেও অতীতের ইজতিহাদ সমূহকে যথেষ্ট গণ্য করে ইজতিহাদের দরযা বন্ধ গণ্য করা। বাছ-বিচার না করে অন্ধভাবে খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছ গ্রহণ করার কারণও তা-ই। ইজতিহাদ অব্যাহত থাকলে এর ধারাক্রমে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এক সময় হাদীছের ক্ষেত্রে এ ভ্রান্ত কর্মনীতির বিলুপ্তি ঘটতে বাধ্য। তাই দেখা যায়, যারা ইজতিহাদ করছেন তাঁরা বহুলাংশে এ অন্ধত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন।
সুন্নীদের মধ্যে যেমন আহলে হাদীছ নামে পরিচিত একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ফির্ক্বাহ্ ইজতিহাদকে অবৈধ গণ্য করে, তেমনি শিয়াদের মধ্যেও আখবারী নামে পরিচিত একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ফির্ক্বাহ্ ইজতিহাদকে অবৈধ গণ্য করে। অন্যদিকে উছূলী নামে পরিচিত বেশীর ভাগ শিয়াদের মধ্যেই ইজতিহাদ প্রচলিত আছে এবং এ ধারার মুজতাহিদগণ ইজতিহাদের ক্ষেত্রে সুন্নী ধারার হাদীছ, তাফসীর ও ফিক্বাহ্ থেকেও সাহায্য নিয়ে থাকেন এবং দেখা গেছে যে, একজন শিয়া মুজতাহিদ কতক ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে শিয়া মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যে চলে আসা পূর্ববর্তী খ্যাতনামা মুজতাহিদগণের ফতোয়া পরিত্যাগ করে সুন্নী ধারার মধ্যে প্রচলিত ফতোয়ার অনুরূপ ফতোয়া দিয়েছেন, কিন্তু এ কারণে তাঁকে কোনোরূপ বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হতে হয় নি। [উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোরআন মজীদের আয়াত انما المشکون نجس অবশ্যই মুশরিকরা অপবিত্র (সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্ ঃ ২৮) এ আয়াতের ভিত্তিতে শিয়া মাযহাবের মুজতাহিদগণের বেশীর ভাগেরই ফতোয়া হচ্ছে এই যে, মূলগতভাবে যে খাবার হালাল তা-ও মুশরিকের দ্বারা প্রস্তুত হলে খাওয়া জায়েয নয়। যদিও অতীতের কতক শিয়া মুজতাহিদ জায়েয বলেছেন, তবে সাধারণভাবে শিয়া মাযহাবের অনুসারীগণ নাজায়েয হওয়ার ফতোয়া অনুযায়ীই আমল করে থাকে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে ক্বোমের দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্রের অন্যতম শিক্ষক আয়াতুল্লাহ্ মুহাম্মাদ জান্নাতী (রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বনামখ্যাত আয়াতুল্লাহ্ আহ্মাদ জান্নাতী নন) তাঁর এক গবেষণামূলক প্রবন্ধে এ বিষয়ে শিয়া-সুন্নী উভয় ধারার হাদীছ ও মুজতাহিদগণের ফতোয়া পর্যালোচনা করে সুন্নী ফতোয়ার অনুরূপ উপসংহারে উপনীত হন যে, সংশ্লিষ্ট আয়াতে শারীরিক অপবিত্রতার (نجسة جسمانی) কথা বলা হয় নি, বরং আত্মিক অপবিত্রতার (نجسة روحانی) কথা বলা হয়েছে, অতএব, বাহ্যতঃ নাপাকীর প্রমাণ বা নিদর্শন না থাকলে হালাল খাবার মুশরিকের দ্বারা প্রস্তুত হলেও তা হালাল। প্রবন্ধটি ক্বোমের দ্বীনী জ্ঞানকেন্দ্রের মুখপত্র کيهان انديشهতে প্রকাশিত হয় এবং এর বিরুদ্ধে কোনো মহল থেকেই কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শিত হয় নি।]
এ পর্যায়ে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে মুসলমানদের শাসন-কর্তৃত্বের বিষয়।
বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ক প্রশ্নটির জবাব সবচেয়ে সহজ বলে মনে করি। কারণ, ছাহাবীদের যুগ অনেক আগেই গত হয়ে গিয়েছে এবং শিয়া মাযহাবের অনুসারীগণ যে বারো জন পবিত্র ব্যক্তিত্বকে আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে মনোনীত ইমাম বলে ‘আক্বীদাহ্ পোষণ করে তাঁদের মধ্যে এগারো জন অনেক আগেই এ পার্থিব দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং শিয়া ‘আক্বীদাহ্ অনুযায়ীই দ্বাদশ ইমাম স্বীয় পরিচিতি ও দাবী সহকারে সমাজে বিচরণ করছেন না, বরং স্বীয় পরিচিতি গোপন করে অবস্থান করছেন। ফলে তাঁর নেতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্বের দাবী মেনে নেয়া বা না মানার প্রশ্নটি আপাততঃ বিদ্যমান নেই। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের প্রশ্নে শিয়া-সুন্নী উভয় ধারার মুসলমানরাই অভিন্ন অবস্থানে এসে উপনীত হয়েছে।
এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে, হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্ববর্তী বর্তমান অন্তর্বর্তীকালে মুসলমানদের শাসনকর্তৃত্বের ভার এমন ব্যক্তিদের হাতে অর্পণ করতে হবে যারা মা‘ছূম না হলেও ইতিপূর্বে উল্লিখিত দ্বীনী নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য তিনটি গুণের অধিকারী। বলা বাহুল্য যে, এ ধরনের গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিত্ব কেবল মুজতাহিদগণের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে। আর কোরআন-সুন্নাহর দাবীও এটাই। কারণ, ইসলামের সকল মাযহাব ও ফির্ক্বাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) থেকে বর্ণিত এমন একটি হাদীছ হচ্ছে ঃ
العلماء ورثة الانبياء.
“আলেমগণ নবী-রাসূলগণের (আঃ) উত্তরাধিকারী।”
আর বলা বাহুল্য যে, এ হাদীছে “আলেম” বলতে বর্তমান যুগে প্রচলিত পরিভাষায় ঢালাওভাবে যাদেরকে “আলেম” বলা হয় তাঁদেরকে বুঝানো হয় নি, বরং কোরআন মজীদে যাদের সম্পর্কে يتفقهوا فی الدين বলা হয়েছে কেবল তাঁদের ক্ষেত্রেই তথা মুজতাহিদগণের ক্ষেত্রেই উল্লিখিত হাদীছের এ শব্দটি প্রযোজ্য। তেমনি এ ধরনের ব্যক্তির জন্য চিন্তা ও আচরণের ক্ষেত্রে ভারসাম্য (‘আদ্ল্ বা তাক্বওয়া)-এর অধিকারী হওয়া তথা চরম পন্থা ও শিথিল পন্থা থেকে মুক্ত হওয়া এবং দূরদৃষ্টির (بصيرة) অধিকারী হওয়াও অপরিহার্য। আর বিচারবুদ্ধির অকাট্য রায়ও এটাকেই সমর্থন করে।
এ বিষয়টি ইসলামে কোনো নতুন বিষয় নয়, যদিও বহু শতাব্দী যাবত বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় নি। অতঃপর খৃস্টীয় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ) এ বিষয়টিকে “ভেলায়াতে ফাক্বীহ্” (ولاية فقيه) মুজতাহিদের শাসন-কর্তৃত্ব) শিরোনামে একটি তত্ত্ব হিসেবে উপস্থাপন করেন। অতঃপর তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইরানের মুসলিম জনগণ ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটানোর পর সেখানে এ তত্ত্ব ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন করে।
দুর্ভগ্যজনক যে, সুন্নী জগতের কতক ইসলামী নেতা ও আলেম “ভেলায়াতে ফাক্বীহ্” তত্ত্বকে শিয়া মাযহাবের একান্ত নিজস্ব বিষয় বলে অভিহিত করে উপেক্ষা করার চেষ্টা করেছেন, অথচ প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, তত্ত্বটির নামের প্রতি দৃষ্টি না দিলেও এর মূল বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, শিয়া মাযহাবের অনুসারীদের অনেক আগে থেকেই (এমনকি হযরত ইমাম খোমেইনী কর্তৃক তত্ত্ব হিসেবে উপস্থাপনেরও বহু আগে হাজার বছরেরও বেশীকাল পূর্ব থেকেই) সুন্নী মাযহাবের অনুসারীরা এ তত্ত্বের মূল বক্তব্যের মুখাপেক্ষী ছিলো।
বস্তুতঃ শিয়া মাযহাবের অনুসারীরা সমাজে মা‘ছূম ইমামগণের প্রকাশ্য উপস্থিতি কালে ইজতিহাদ ও “ভেলায়াতে ফাক্বীহ্” তত্ত্ব কোনোটিরই মুখাপেক্ষী ছিলো না। কারণ, মা‘ছূম (নবীই হোন বা ইমামই হোন) যখন সমাজে উপস্থিত থাকেন তখন দ্বীনী জিজ্ঞাসার চূড়ান্ত জবাব দানের অধিকার এবং শাসন-কর্তৃত্বের অধিকার একমাত্র তাঁরই; কেবল মা‘ছূমের অনুপস্থিতিতেই ইজতিহাদ ও “ভেলায়াতে ফাক্বীহ্”র প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু সুন্নী ‘আক্বীদাহ্ অনুযায়ী যেহেতু হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ওফাতের সাথে সাথে ‘আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে মনোনীত’ দ্বীন-ব্যাখাকারী এবং নেতা ও শাসনকর্তার সমাপ্তি ঘটেছে সেহেতু يتفقهوا فی الدين সম্বলিত আয়াত ও العلماء ورثة الانبياء. হাদীছ অনুযায়ী, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওফাতের পর মুহূর্ত থেকেই তাদের জন্য ওলামা তথা মুজতাহিদগণের দ্বীনী নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্ব অপরিহার্য হয়ে ওঠে।
এ ক্ষেত্রে দ্বীনের ব্যাখ্যা ও শাসন-কর্তৃত্বের জন্য হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ছাহাবী, তাবে‘ঈন্ বা তাবে‘ তাবে‘ঈন্-এর কথা চিন্তা করা হলে তা একটি তত্ত্ব হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ, তাঁরা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রজন্ম মাত্র। অন্যদিকে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর স্থলাভিষিক্ততার প্রশ্নটি কোনো সাময়িক প্রশ্ন নয়, বরং তাঁর ওফাতের পর মুহূর্ত থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত একটি স্থায়ী প্রশ্ন। তাই আল্লাহর মনোনীত স্থলাভিষিক্ততা তথা ইমামতের ‘আক্বীদাহ্ গ্রহণ না করলে তত্ত্ব হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর স্থলাভিক্তিতার বিষয়টি ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রশ্নের উর্ধে চিন্তা করতে হবে এবং “ভেলায়াতে ফক্বীহ্” তত্ত্বটি এ ধরনেরই একটি তত্ত্ব। আর এ তত্ত্ব ছাহাবী, তাবে‘ঈন্ বা তাবে‘ তাবে‘ঈন্ সহ যে কোনো প্রজন্মের জন্য প্রযোজ্য।
বস্তুতঃ বাস্তবে মুসলমানদের একজন দ্বীনী নেতা ও শাসক বা খলীফাহ্ “ভেলায়াতে ফাক্বীহ্”র জন্য অপরিহার্য গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন কিনা তা একটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন যা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু একজন দ্বীনী নেতা ও শাসকের জন্য যে এর সবগুলো গুণের অধিকারী হওয়া অপরিহার্য সে ব্যাপারে বিতর্ক থাকতে পারে না।
এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, অতীতে সুন্নী জগতের মনীষীগণও যে এ বিষয়টির প্রতি মোটেই দৃষ্টি দেন নি তা নয়। কারণ, তাঁদের অনেকে খলীফাহ্ বা শাসক মনোনয়নের এখতিয়ার اهل الحل والعقد (দ্বীনী বিষয়াদিতে চূড়ান্ত মতামত প্রদানের যোগ্যতার অধিকারীগণ)-এর বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।
মোদ্দা কথা, আজকের দিনে শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে মুসলিম সমাজের দ্বীনী নেতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্বের একমাত্র সমাধান হচ্ছে “ভেলায়াতে ফাক্বীহ্” বা ‘মুজতাহিদের শাসন-কর্তৃত্ব’।
হযরত ইমামে খোমেইনী (রহ্ঃ) কেবল যে এ তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন তা নয়, তিনি এর প্রায়োগিক পদ্ধতিও প্রদর্শন করে গেছেন। যেহেতু কোরআন মজীদের যে আয়াত ও হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর যে হাদীছ এ তত্ত্বের ভিত্তি তাতে মাত্র একজন আলেম বা মুজতাহিদকে দ্বীনী নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্বের অধিকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয় নি, বরং উভয় সূত্রেই বহুবচন বাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেহেতু এ অধিকার ও দায়িত্ব সমাজে বিদ্যমান সকল মুজতাহিদের। তবে যেহেতু রাষ্ট্রক্ষমতার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব কেবল একজনের ওপরই ন্যস্ত করা যেতে পারে সেহেতু তাঁরা তাঁদের শাসনকর্তৃত্বের দায়িত্বটি নিজেদের মধ্য থেকে একজনের ওপর অর্পণ করবেন।
কিন্তু এ অর্পণের মানে শাসনকর্তৃত্বের ক্ষেত্রে তাঁদের অধিকার ও কর্তব্যের পরিসমাপ্তি ঘটা নয়। সুতরাং তাঁরা সব সময়ই শাসকের কাজের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন ও তাঁকে পরামর্শ দেবেন এবং শাসক যদি কখনো শারীরিক, মানসিক, নৈতিক বা রাজনৈতিক দিক থেকে যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন তাহলে তাঁরা যে কোনো মুহূর্তে তাঁকে অপসারিত করে তাঁর স্থলে অন্য কারো ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করতে পারবেন।
অন্যদিকে দ্বীনী বিষয়াদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অধিকার ও কর্তব্য সর্বাবস্থায়ই ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মুজতাহিদেরই থাকবে এবং এ ক্ষেত্রে তাঁদের প্রত্যেকের অনুসারীগণ নিজ নিজ অনুসৃত মুজতাহিদকেই অনুসরণ করতে থাকবে; রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রেই শাসক-মুজতাহিদের মতের অনুসরণ সকলের জন্য বাধ্যতামূলক হবে না। শুধু তা-ই নয়, যে সব বিষয়ে রাষ্ট্রের বাস্তবায়ন-কর্তৃত্ব বা বিচারিক কর্তৃত্ব থাকে এমন বিষয়াদিতেও যদি বিভিন্ন মাযহাব বা বিভিন্ন মুজতাহিদের রায়ের মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে মতপার্থক্য থাকে (যেমন ঃ বিবাহ-তালাক্ব ও মীরাছ বণ্টনের ক্ষেত্রে কতক শাখাগত বিষয়) সে সব ক্ষেত্রেও সকলের ওপরে শাসক-মুজতাহিদের মত বা সংখ্যাগুরু মাযহাবের রায় চাপিয়ে দেয়া যাবে না। বরং বিবদমান পক্ষদ্বয় একই মাযহাবের বা একই মুজতাহিদের অনুসারী হলে তাদের ব্যাপারে তাদের অনুসৃত মাযহাব বা মুজতাহিদের রায় অনুযায়ী ফয়সালা করতে হবে, তবে বিবদমান পক্ষদ্বয় যদি দুই ভিন্ন মাযহাব বা মুজতাহিদের অনুসারী হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট জনপদে যারা সংখ্যাগুরু তাদের ফিক্বহী রায় অনুযায়ী ফয়সালা করতে হবে।
অমুসলিম সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রেও এ নীতিই প্রযোজ্য হবে।
অবশ্য ফৌজদারী দণ্ডবিধি, পররাষ্ট্রনীতি, সশস্ত্র বাহিনী, যুদ্ধ, সন্ধি, আমদানী-রফতানী নীতি, মুদ্রানীতি ইত্যাদি একান্তভাবেই মুজতাহিদ শাসকের এখতিয়ারাধীনে থাকবে যে সব ক্ষেত্রে তিনি তাঁকে নির্বাচনকারী মুজতাহিদগণের এবং তাঁকে সহায়তাকারী আইন বিভাগ, প্রশাসন ইত্যাদির সাহায্যক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রশাসন ও স্বাধীন বিচার বিভাগের মাধ্যমে কার্যকর করবেন। বস্তুতঃ এর চেয়ে উত্তম ও ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা চিন্তা করা সম্ভব নয়।
এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ) স্বয়ং শিয়া মাযহাবের অনুসারী একজন মুজতাহিদ ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে “ভেলায়াতে ফাক্বীহ্” তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন তা শিয়া-সুন্নী যে কোনো দেশে সমানভাবে প্রযোজ্য; এ তত্ত্ব প্রয়োগের জন্য শিয়া মাযহাবের অনুসারী কোনো মুজতাহিদকে শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করা জরুরী নয়। বরং সুন্নী মুসলমানদের দ্বারা অধ্যুষিত কোনো দেশে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার শাসনকর্তৃত্ব সে দেশেরই কোনো মুজতাহিদের ওপর অর্পিত হবে। [যদিও বর্তমান প্রেক্ষাপটে সুন্নী সমাজে ইজতিহাদের দরযা বন্ধ গণ্য করার কারণে কোনো মুজতাহিদ নেই, কিন্তু এখানে যা আলোচনা করা হয়েছে কোনো সমাজে তা গ্রহণযোগ্য হিসেবে পরিগণিত হলে ফরযে কেফায়ী হিসেবে অবশ্যই সেখানে ইজতিহাদ শুরু হবে এবং এরই ধারাবাহিকতায় এক সময় হয়তো সেখানে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা “ভেলায়াতে ফাক্বীহ্” তত্ত্ব বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। অতএব, সুন্নী সমাজে কোনো শিয়া মুজতাহিদকে এনে শাসনকর্তৃত্ব দিতে হবে বা ইরান থেকে কোনো মুজতাহিদকে ধার করে এনে শাসনকর্তৃত্বে বসাতে হবে এমনটি মনে করার কোনো কারণ নেই। তার চেয়েও বড় কথা এই যে, সুন্নী সমাজে ইজতিহাদের ধারা পুনঃপ্রবর্তিত হলে বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে যে শিয়া-সুন্নী বিভক্তি ও ব্যবধান রয়েছে তার পুরোপুরি বিলুপ্তি না ঘটলেও ‘প্রায় বিলুপ্তি’ ঘটবে। কারণ, একজন প্রকৃত মুজতাহিদ মাযহাবী সঙ্কীর্ণতার উর্ধে থেকে সত্যকে উদ্ঘাটন করেন এবং তিনি সত্য হিসেবে যে উপসংহারে উপনীত হন তা-ই সমাজের কাছে পেশ করেন।]